আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পরিচিতি
Table of Contents
বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পরিচিতি
বাংলাদেশের ভৌগোলিক অঞ্চলে নানা ধরনের জলাশয় রয়েছে। তবে ধরন অনুযায়ী এসব জলাশয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-
(ক) স্বাদু পানি
(খ) লোনা পানি এবং
(গ) খাড়ি এলাকা।
উপরোক্ত জলাশয়সমূহে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। অনেক সময় এক ধরনের জলাশয়ের মাছ অন্য ধরনের জলাশয়ে পাওয়া গেলেও প্রায় প্রতিটি জলাশয়ের পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে মাছের ধরনও কিছুটা পৃথক হয়। নিচে বিভিন্ন জলাশয় কি কি প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় তা উল্লেখ করা হলো :
(ক) স্বাদু পানির মাছের প্রজাতি
বাংলাদেশের স্বাদু পানির পরিবেশে যেসব জলাশয়কে চিহ্নিত করা হয়, তার মধ্যে নদ-নদী, খাল-বিল, দিঘি, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি অন্যতম। এসব জলাশয়ে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো মাছ ছাড়াও অনেকক্ষেত্রে মাছ চাষাবাদ করা হয়।
মাছের যেসব প্রজাতি এক্ষেত্রে চাষাবাদ করা হয়, তার মধ্যে রুই জাতীয় মাছ, যেমন- কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউশ প্রধান। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ জাতীয় মাছ খুব বেশি চাষাবাদ করা হয়। পূর্বে এ জাতীয় মাছ স্বাদু পানির বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও বর্তমানে এর পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ায় এসবের চাষাবাদ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এছাড়া অন্যান্য মাছের মধ্যে বিদেশী রুই জাতীয় মাছ যেমন- সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প, মা কার্প, কার্পিও, শোল, গজার, টাকি, মাগুর, শিং, কৈ, মলা, ঢেলা, বিভিন্ন প্রজাতির পুঁটি মাছ ইত্যাদি প্রধান। এসব মাছের মধ্যে শিং, কৈ, ঢেলা, মলা, মাগুর ইত্যাদি মাছ ছোট আকারের জলাশয়ে বেশি চাষাবাদ করা হয়।
(খ) লোনাপানির মাছের প্রজাতি
লোনা পানির পরিবেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের লোনা পানির পরিবেশ অন্যতম। এ অঞ্চলে নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। তবে এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাছ হলো, বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ, রূপচান্দা, ছুরি, দাতিনা, পোয়া, কোড়াল, লইট্যা, বিভিন্ন প্রজাতির হাঙর, ইত্যাদি।
(গ) খাড়ি এলাকার মাছের প্রজাতি :
বাংলাদেশের খাড়ি এলাকা হলো বিভিন্ন নদীর মোহনা। এসব অঞ্চলেও নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ হলো : ভেটকি, পোয়া ইত্যাদি।

চাষোপযোগী মাছ
বাংলাদেশের জলাশয়সমূহের নানা প্রজাতির মাছের মধ্যে সবগুলোই কিন্তু চাষোপযোগী নয়। তবে অনেক প্রজাতির মাছই বিভিন্ন জলাশয়ে চাষাবাদ করা যেতে পারে। পরিচিত অনেক মাছই চাষাবাদের উপযোগী নয়। কোন কোন প্রজাতির মাছ বাংলাদেশের জলাশয়ে চাষোপযোগী, মৎস্যবিজ্ঞানীরা তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। বাংলাদেশের অতি পরিচিত মাছের মধ্যে কোনগুলো চাষোপযোগী আর কোনগুলো চাষোপযোগী নয়, তা পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো।
চাষোপযোগী মাছ
রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প, কমন কার্প, নাইলোটিকা, তেলাপিয়া, রাজপুঁটি, পাঙ্গাস, বিদেশী মাগুর, দেশী মাগুর, শিং, সরপুঁটি ইত্যাদি। কোড়াল ইত্যাদি।
চাষোপযোগী নয় এমন মাছ
চান্দা, ইলিশ, লহরো হাঙর, ছবি, বেলে, দাতিনা,
চাষোপযোগী মাছের গুণাগুণ
চাষোপযোগী মাছের বিভিন্ন ধরণের গুণাগুণ রয়েছে। কোন মাছ চাষোপযোগী কিনা তা তিনটি মূল বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এসব বিষয় হলো (ক) মাছের বৈশিষ্ট্য (খ) চাষাবাদের উপযোগিতা এবং (গ) মাছের উপযোগিতা। নিচে এসব বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো :
(ক) মাছের বৈশিষ্ট্য
(১) মাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে
(২) জলাশয়ে স্থান ও খাদ্যের জন্য অন্য মাছের সাথে কোন প্রতিযোগিতা করে না বা করলেও তেমন মারাত্মক নয় ।
(৩) সহজে কোনপ্রকার রোগ ও পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয় না।
(৪) প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও সম্পূরক খাদ্য সহজেই গ্রহণ করতে পারে।
(খ) চাষাবাদগত উপযোগিতা
(১) কম স্থানে বেশি সংখ্যায় চাষাবাদ করা যায়।
(২) প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সহজেই মাছের পোনা পাওয়া যায়।
(৩) কৃত্রিম উপায়ে মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।
(৪) পোনা পরিবহন করা সহজ।
(গ) মাছের উপযোগিতা
(১) খেতে সুস্বাদু।
(২) বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।
যেসব মাছে উল্লেখিত গুণাগুণ রয়েছে, সাধারণভাবে সেসব মাছই চাষোপযোগী মাছ হিসেবে চিহ্নিত।
বিভিন্ন চাষোপযোগী মাছ পরিচিত
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জলাশয়ে নানা প্রজাতির চাষোপযোগী মাছ রয়েছে। এসব মাছের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাছের বিস্তারিত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :
(১) কার্প জাতীয় মাছ
দেশী ও বিদেশী রুই জাতীয় মাছকে সাধারণভাবে কার্প নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য কার্পকে আবার মেজর কার্প এবং মাইনর কার্প-এই দুভাগে ভাগ করা হয়। দেশী মেজর কার্পের মধ্যে উলেখযোগ্যগুলো হলো বুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবাউশ, অন্যদিকে বিদেশী মেজর কার্পের মধ্যে কার্পিও, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, কমন কার্প ইত্যাদি প্রধান। অন্যদিকে মাইনর কার্পের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির পুঁটি মাছ, যেমন- সরপুঁটি, জাতিপুঁটি, চোলাপুঁটি, ইত্যাদি প্রধান। কার্প জাতীয় মাছ সাধারণত জলাশয়ের বিভিন্ন স্তর (যেমন উর্ধ্বস্তর, মধ্যস্তর এবং নিম্নস্তর) থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।
এসব মাছ একক এবং মিশ্রভাবে চাষাবাদ করা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন পুকুরের সব খাবার সমানভাবে ব্যবহৃত হয় তেমনি জলাশয়ের পরিবেশও ভালো থাকে। বাংলাদেশে কার্প জাতের মাছ একক বা মিশ্র পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে চাষাবাদ হয়ে থাকে। এ পাঠে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু চাষোপযোগী কার্প মাছের বর্ণনা দেওয়া হলো। এক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী মাছের পরিচিতি পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো।
দেশী চাষযোগ্য মাছ
এ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম Labeo rohita। রুই মাছ সাধারণত স্বাদু পানির বাসিন্দা। এ মাছ বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি-ডোবাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ মাছ খাদ্য হিসেবে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এর বাজার মূল্যও যথেষ্ট।
এটি দেশের অন্যতম চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃত। দেহগঠন রুই মাছের দেহ লম্বাটে এবং স্রোতমুখীন। এই মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় কিছুটা ছোট। দেহের উপরিভাগের তুলনায় দেহের নিচের অংশ খানিকটা বাঁকানো।
রুই মাছের পিঠের দিকের রং কিছুটা বাদামি হলেও পেটের উভয় দিকের রং হালকা সোনালী বর্ণের। রুই মাছের ঠোঁট বেশ পুরু, ঠোঁটের কিনারা বা প্রান্তভাগে বেশ কিছু সূক্ষ্ম খাঁজ রয়েছে। ঠোঁটের আগায় একজোড়া ছোট কিন্তু মাংসল শুঁড় রয়েছে। এ মাছের লেজ বেশ ভালোভাবে দ্বিখন্ডিত এবং খানিকটা ছড়ানো ধরনের।
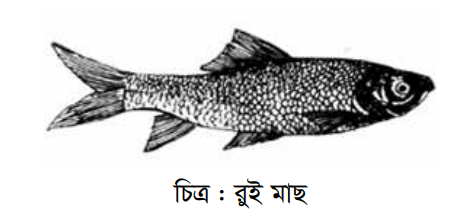
খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস:
রুই মাছের প্রধান খাদ্য জলাশয়ে অবস্থানরত বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যাংকটন। এরা সাধারণত জলাশয়ের মধ্যস্তর থেকে খাবার গ্রহণ করে থাকে। মূলত এ কারণে রুই মাছকে স্তরভোজী (column feeder) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে বিজ্ঞানীদের মতে, প্রয়োজনে রুই মাছ খাদ্যের সন্ধানে জলাশয়ের ঊর্ধ্ব এবং নিম্নস্তরেও গমন করতে পারে।
উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যাংকটন ছাড়াও রুই মাছ জলাশয়ে জন্মানো নানা ধরনের উদ্ভিদের পাতা, পঁচা জৈব আবর্জনা খেয়ে থাকে। চাষ করা হয় এমন ধরনের জলাশয়ে রুই মাহ জলাশয়ে প্রাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে সরবরাহ করা সম্পূরক খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। এসব সম্পূরক খাদ্যে ভিটামিনসহ উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে।
পরিপক্বতা বা বংশবিস্তার
রুই মাছ সাধারণত বদ্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। প্রজননের জন্য রুই মাছের বিশেষ কিছু পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার প্রয়োজন হয়। এসব যথাযথভাবে না হলে রুই মাছের প্রজনন সার্থকভাবে সম্পাদন করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশে রুই মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।
তিন বছর বয়সে এ মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ২ থেকে ৩ লক্ষ ডিম ধারণ করতে পারে। সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত রুই মাছ ডিম পাড়ে। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে রুই মাছের পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে।
কাতলা
এ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম Catla catla কাতলা মাছ রুই মাছের মতোই স্বাদু পানির বাসিন্দা। এ মাছ বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি-ডোবাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ মাছ খাদ্য হিসেবে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট। এটি দেশের অন্যতম প্রধান চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃত।
দেহগঠন
কাতলা মাছের দেহ লম্বাটে এবং স্রোতমুখীন। এ মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় বেশ বড়, অনেকক্ষেত্রে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কাতলা মাছের দেহ চওড়া এবং খানিকটা চ্যাপ্টা ধরনের। পিঠের দিকের রং ধূসর, পেটের দিকের রং সাদাটে।
দেহের উপরিভাগ খানিকটা বাঁকানো। কাতলা মাছের পিঠের দিকের রং কিছুটা কালচে বর্ণের। কাতলা মাছের ঠোঁট বেশ পুরু, উপরের দিকে বাঁকানো এবং প্রাসরণক্ষম। এ মাছের লেজ বেশ ভালোভাবে দ্বিখন্ডিত এবং খানিকটা ছড়ানো ধরনের।

খাদ্য ও খাদ্যভ্যাস :
কাতলা মাছের প্রধান খাদ্য জলাশয়ে অবস্থিত নানা ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্ল্যাংকটন। এরা সাধারণত জলাশয়ের উপরের স্তর থেকে খাবার গ্রহণ করে থাকে। মূলত এ কারণে কাতলা মাছকে ঊর্ধ্বরভোজী (surface feeder) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
ছোট অবস্থায় কাতলা মাছ প্রাণী প্ল্যাংকটন এবং বড় অবস্থায় উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ও খোলসযুক্ত ছোট ছোট প্রাণী খেয়ে থাকে। চাষ করা হয় এমন ধরনের জলাশয়ে কাতলা মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে সরবরাহ করা সম্পূরক খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। এসব সম্পূরক খাদ্যে ভিটামিনসহ উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে ।
পরিপক্বতা ও বংশবিস্তার:
কাতলা মাছের মতোই বন্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। প্রজননের জন্য কাতলা মাছের বিশেষ কিছু পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার প্রয়োজন হয়। এসব যথাযথভাবে না হলে কাতলা মাছের প্রজনন সার্থকভাবে সম্পাদন করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশে কাতলা মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।
তিন থেকে পাঁচ বছরের বয়সে এ মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ১৫ থেকে ৩০ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে। সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত কাতলা মাছ ডিম পাড়ে। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে কাতলা মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ চলছে।
মৃগেল মাছ
এ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম Cirhinus mrigala মৃগেল মাছ রুই মাছের মতোই স্বাদু পানির বাসিন্দা। মৃগেল মাছ বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাগুড়, খাল-বিল, পুকুর-ডোবাতে
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ মাছ খাদ্য হিসেবে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট। এটি দেশের অন্যতম প্রধান চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃত।
দেহগঠন :
মৃগেল মাছের দেহ লম্বাটে এবং স্রোতমুখীন। এই মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় বেশ ছোট। মৃগেল মাছের দেহ খানিকটা চ্যাপ্টা ধরনের। দেহের রং তামাটে বর্ণের তবে উভয় পাশে ও পেটের দিকের রং সোনালী। দেহের পৃষ্ঠভাগ খানিকটা বাঁকানো ধরনের। মৃগেল মাছের পাখনাগুলো কিছুটা লালচে বর্ণের। মৃগেল মাছের ঠোঁট নিচের দিকে বাঁকানো এবং ঠোঁটের দুপাশে একজোড়া গুঁড় রয়েছে।
খাদ্য ও খাদ্যাভাস
মৃগেল মাছের প্রধান খাদ্য জলাশয়ের তলদেশে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের পদার্থ মূলত এ কারণে মৃগেল মাছকে নিম্নস্তরভোজী (bottom feeder) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ছোট অবস্থায় মৃগেল মাছ প্রাণী প্ল্যাংকটন এবং বড় অবস্থায় জলাশয়ের তলদেশের নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ, পচা আবর্জনা, কাদার মধ্যে জন্মানো বিভিন্ন ধরনের কীট, যাদের বেনথোস বলা হয় ইত্যাদি খেয়ে থাকে। চাষ করা হয় এমন ধরনের জলাশয়ে মৃগেল মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে সরবরাহ করা সম্পূরক খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। এসব সম্পূরক খাদ্যে ভিটামিনসহ উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে।
পরিপক্বতা ও বংশবিস্তার।
মৃগেল মাছ রুই মাছের মতোই বন্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। প্রজননের জন্য মৃগেল মাছের বিশেষ কিছু পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার প্রয়োজন হ্যা। এসব যথাযথ না হলে মৃগেল মাছের প্রজনন সার্থকভাবে সম্পাদন করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশে মৃগেল মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় ৮ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। দুই বছর বয়সে এই মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে।
একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ১ থেকে ৫ লাখ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে। সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্যন্ত মৃগেল মাছ ডিম পাড়ে। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে মৃগেল মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ চলছে।
কালবাউস মাছ
এ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম Labeo cailbasu কালবাউস মাছ রুই- কাতলা-মৃগেল মাছের মতোই স্বাদু পানির বাসিন্দা। বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি-ডোবাতে প্রচুর পরিমাণে কালবাউস মাছ পাওয়া যায়। এ মাছ খাদ্য হিসেবে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এর অর্থনৈতিক মূল্য থাকায় এটি দেশের অন্যতম প্রধান চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে।
দেহগঠন
কালবাউস মাছের দেহ লম্বাটে এবং স্রোতমুখীন। কালবাউস মাছ দেখতে অনেকটা মৃগেল মাছের মতো। এ মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় বেশ ছোট। কালবাউস মাছের দেহ খানিকটা চ্যাপ্টা ধরনের। দেহের রং তামাটে বর্ণের তবে উভয় পাশে ও পেটের দিকের রং ধূসর সাদা কালবাউস মাছের পাখনাগুলো কিছুটা কালচে বর্ণের। এ মাছের আঁইশগুলোর মাঝের অংশ সামান্য লাল কিন্তু কিনারগুলো কালচে বর্ণের। কালবাউস মাছের মুখ সরু এবং মুখে দুই জোড়া ছোট গোঁফ রয়েছে।
খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস :
কালবাউস মাছ মৃগেল মাছের মতোই জলাশয়ের তলদেশে বসবাস করে। এ মাছের প্রধান খাদ্য জলাশয়ের তলদেশে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের পদার্থ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মূলত এ কারণে কালবাউস মাছকেও নিম্নস্তরভোজী (bottom feeder ) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
ছোট অবস্থায় কালবাউস মাছ প্রাণী প্ল্যাংকটন এবং বড় অবস্থায় জলাশয়ের তলদেশের নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ, পচা আবর্জনা, কাদার মধ্যে জন্মানো বিভিন্ন পরনের কীট, যাদের লেনথোস বলা হয় ইত্যাদি খেয়ে থাকে। চাষ করা হয় এমন ধরনের জলাশয়ে কালবাউস মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে সরবরাহ করা সম্পূরক খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। এসব সম্পূরক খাদ্যে ভিটামিনসহ উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে। এক কথায় কালবাউস মাছকে সর্বভুক মাছ বলা যায়।
পরিপক্বতা ও বংশবিস্তার:
কালবাউস মাছ রুই-কাতলা-মৃগেল মাছের মতোই বদ্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। প্রজননের জন্য কালবাউস মাছের বিশেষ কিছু পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার প্রয়োজন হয়। এসব যথাযথ না হলে কালবাউস সার্থকভাবে প্রজনন কাজ সম্পাদন করতে পারে না।
প্রাকৃতিক পরিবেশে কালবাউস মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় ৭ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। দুই বছর বয়সে কালবাউস মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ২ থেকে ৬ লাখ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে।
সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কালবাউস মাছ নদ-নদীতে প্রজনন করে ডিম পাড়ে বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশে কালবাউস মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ চলছে।
বিদেশী চাষযোগ্য মাছ
সিলভার কার্প
এ মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Hypothalmicthyes molitrix। সিলভার কার্প রুই-কাতলা- মৃগেল মাছের মতোই স্বাদু পানির বাসিন্দা। এটি মূলত চীন এবং রাশিয়ার নদ-নদীর মাছ। ১৯৬৯ সালে সিলভার কার্প সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আনা হয় এবং পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে এর চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি-ডোবাতে প্রচুর পরিমাণে সিলভার কার্প মাছ পাওয়া যায়। এ মাছ খাদ্য হিসেবে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এর অর্থনৈতিক মূল্যও রয়েছে। এটি সহজেই বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে।
দেহগঠন :
সিলভার কার্প মাছের দেহ লম্বাটে এবং স্রোতমুখীন। সিলভার কার্প মাছের দেহের নিচের অংশ অনেকটা নৌকার মতো দেখতে। এই মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় বেশ ছোট। সিলভার কার্প মাছের দেহ খানিকটা চ্যাপ্টা ধরনের এবং ছোট অবস্থায় দেখতে অনেকটা চাপিলা মাছের মতো।
তবে মাঝারি অবস্থায় এ মাছ দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মতো। দেহের উপরিভাগের রং কিছুটা কালচে বর্ণের হলেও দেহের উভয় পাশ ও পেটের দিকের রং খানিকটা ধূসরাভ রূপালী সিলভার কার্প মাছের দেহের আঁইশসমূহ ছোট এবং রূপালী বর্ণের।
খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস :
সিলভার কার্প মাছের খাদ্যাভ্যাস অনেকটা দেশী মাছ কাতলার মতো। এর জলাশয়ের ঊর্ধ্বস্তরে বসবাস করে। এই মাছের প্রধান খাদ্য জলাশয়ের ঊর্ধ্বস্তরে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন। মূলত এ কারণে সিলভার কার্প মাছকেও ঊর্ধ্বস্তরভোজী মাছ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
ছোট অবস্থায় সিলভার কার্প মাছ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যাংকটন এবং বড় অবস্থায় জলাশয়ের নানা প্রজাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল ও পচা জলজ উদ্ভিদ খায়। চাষ করা হয় এমন জলাশয়ে সিলভার কার্প মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে সরবরাহ করা সম্পূরক খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। এসব সম্পূরক খাদ্যে ভিটামিনসহ উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে।
পরিপক্বতা ও বংশবিস্তার
সিলভার কার্প মাছ রুই-কাতলা-মৃগেল মাছের মতোই বন্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। প্রজননের জন্য সিলভার কার্প মাছের বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন হয়। এসব যথাযথভাবে না হলে সিলভার কার্প সার্থকভাবে প্রজনন কাজ সম্পাদন করতে পারে না। প্রাকৃতিক পরিবেশে সিলভার কার্প মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় ৭ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।
প্রায় দেড় বছর বয়সে সিলভার কার্প মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ৬ থেকে ৮ লাখ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে। সাধারণত আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সিলভার কার্প মাছ নদ- নদীতে প্রজনন করে ও ডিম পাড়ে। ১৯৭৬ সালে এই মাছের কৃত্রিম প্রজনন সার্থকভাবে সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে সিলভার কার্প মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ চলছে।
গ্রাস কার্প
এ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম Ctenopharyngodon idella। গ্রাস কার্প মাছ রুই-কাতলা- মৃগেল মাছের মতোই স্বাদু পানির বাসিন্দা। এ মাছের মূল আবাসস্থল চীন এবং রাশিয়ার নদ- নদী। ১৯৯৬ সালে গ্রাস কার্প মূলত জলাশয়ের জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আনা হয় এবং পরবর্তীকালে এদেশে ব্যাপকভাবে এর চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে।
বর্তমানে বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর- দিঘি-ডোবাতে প্রচুর পরিমাণে গ্রাস কার্প মাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এটি ঘেসো রুই নামে পরিচিত। এ মাছ খাদ্য হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। এর যথেষ্ট অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে। ফলে এটি খুব সহজেই বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। দেহগঠন গ্রাস কার্প মাছের দেহ বেশ লম্বাটে ধরনের এবং স্রোতমুখীন।
গ্রাস কার্প মাছের দেহ দেখতে অনেকটা মৃগেল মাছের মতো। এদের পিঠের রং তামাটে হলেও দেহের অন্য অংশের রং ঈষৎ সবুজাভ ধরনের। গ্রাস কার্প মাছের পাখনা ছোট ধরনের। এই মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় বেশ ছোট। গ্রাস কার্প মাছের দেহ বেশ চ্যাপ্টা এবং দেহ মাঝারি আকারে আঁইশ দিয়ে আবৃত। গ্রাস কার্প মাছের দেহের আঁইশসমূহ মাঝারি আকারের এবং রূপালী।
খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস :
গ্রাস কার্প মাছের খাদ্যাভ্যাস ছোটবেলায় অনেকটা দেশী অন্যান্য মাছের মতোই। এসময় এরা উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন খেয়ে থাকে। তবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের খাদ্যাভ্যাসও পরিবর্তিত হয়। ছোট অবস্থায় গ্রাস কার্প মাছ জলজ উদ্ভিদ ও ঘাসের কচি পাতা খেতে অভ্যস্থ এবং বড় অবস্থায় জলাশয়ের বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস খেতে অভ্যস্থ।
চাষ করা হয় এমন ধরনের জলাশয়ে গ্রাস কার্প মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদের পাশাপাশি বাইরে থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদের টুকরো করা অংশ সরবরাহ করা হয়। পরিপক্বতা ও বংশবিস্তার: গ্রাস কার্প মাছ অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের মতোই বন্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। বর্ষাকালে এটি প্রজনন করে।
প্রজননের জন্য গ্রাস কার্প মাছের বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে গ্রাস কার্প মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় ৭ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। প্রায় দেড় বছর বয়সে গ্রাস কার্প মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ৬ থেকে ৮ লাখ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে।
সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে গ্রাস কার্প মাছ নদ- নদীতে প্রজনন করে ও ডিম পাড়ে। ১৯৮৩ সালে এই মাছের কৃত্রিম প্রজনন সার্থকভাবে সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে গ্রাস কার্প মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ চলছে। এসব মাছ ছাড়াও বাংলাদেশে আরও কিছু মাছ চাষযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত। এসব মাছের মধ্যে কমন কার্প প্রধান।
সারমর্ম
• বাংলাদেশের জনসম্পদ তিন ভাগে বিভক্ত।
• চাষযোগ্য মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং খেতে সুস্বাদু। বুই, কাতলা, মৃগেল ও কালবাউস উল্লেখযোগ্য চাষযোগ্য দেশী মাছ।
• চাষযোগ্য বিদেশী মাছের মধ্যে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কমন কার্প উল্লেখযোগ্য।
