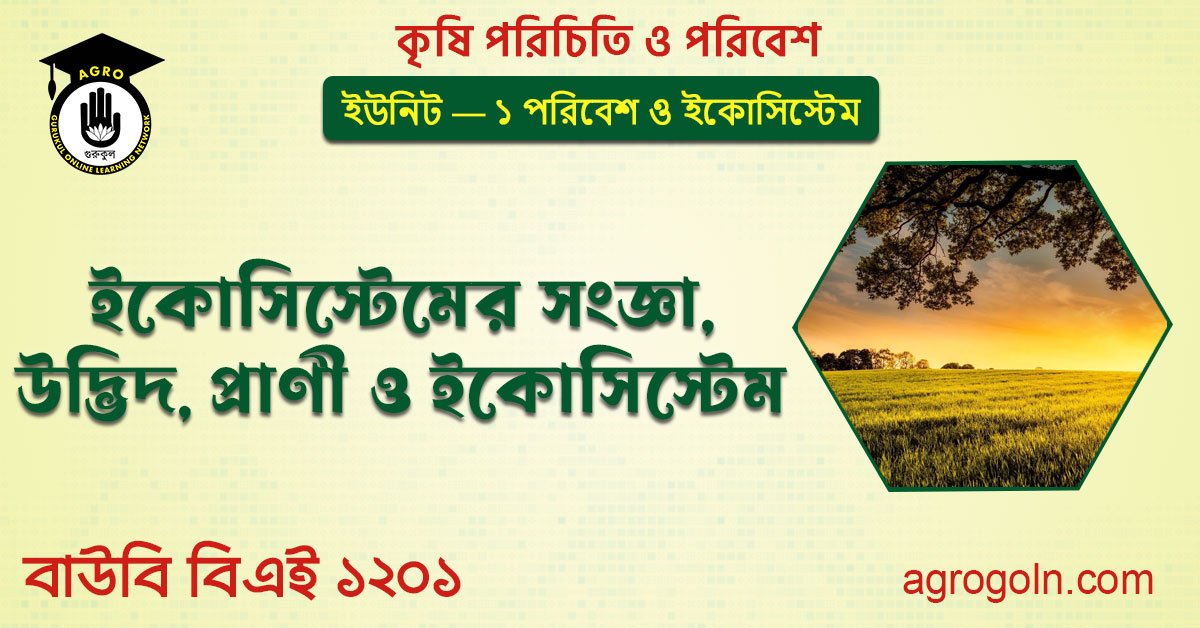ইকোসিস্টেমের সংজ্ঞা, উদ্ভিদ, প্রাণী ও ইকোসিস্টেম , কৃষি পরিচিতি ও পরিবেশ – নিয়ে আজকের আলোচনা। এই পাঠটি “কৃষি পরিচিতি ও পরিবেশ” বিষয়ের “পরিবেশ” বিভাগের ১ নং ইউনিটের ১.৫ নং পাঠ।
Table of Contents
ইকোসিস্টেমের সংজ্ঞা, উদ্ভিদ, প্রাণী ও ইকোসিস্টেম

কোন জীবই পৃথিবীতে অবিমিশ্র অবস্থায় বাস করতে পারে না। প্রায় সকল জীবই একদিকে তার পরিবেশ অন্যদিকে অন্যান্য জীবের সাথে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। বিভিন্ন জাতের জীবের এরূপ সমষ্টিগত বসবাসরীতিকে জীব—স¤প্রদায় বলে। আবার জীব—সম্প্রদায় এবং অজৈব পরিবেশের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া—বিক্রিয়া দ্বারা একটি অবিচ্ছেদ্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় যার নাম ইকোসিস্টেম। এ.জি. টেনসলি (১৯৩৫) নামে একজন বৃটিশ পরিবেশ বিজ্ঞানী প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। পরে সুকাচেভ নামক একজন রুশ পরিবেশ বিজ্ঞানী এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইকোসিস্টেম হচ্ছে একটি গতিময় পদ্ধতি যেখানে জীব ও জড় উপাদানের মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্রিয়াবিক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের গঠন ও কার্যের পরিবর্তন ঘটছে।
ইকোসিস্টেমের সংজ্ঞা :
ইকোসিস্টেম (Ecosystem) একটি ইংরেজি শব্দ। এর বাংলা প্রতিশব্দ বাস্তুতন্ত্র। বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম হচ্ছে জৈব, অজৈব পদার্থ ও বিভিন্ন জীবসমন্বিত এমন প্রাকৃতিক একক যেখানে বিভিন্ন জীবসমষ্টি পরস্পরের সাথে এবং তাদের পারিপার্শ্বিক জৈব ও অজৈব উপাদানের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জীবনধারা গড়ে তোলে।
ই. পি. ওডামের মতে:
ইকোসিস্টেম বলতে জীব, প্রকৃতি ও তাদের আনুষঙ্গিক উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিক্রিয়ার মূল কার্যকর একককে বুঝায়। কিন্তু, এস. মাথাভান (১৯৭৪) এর মতে, জীব ও তার পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া—বিক্রিয়ার পদ্ধতিকে ইকোসিস্টেম বলে।

ইকোসিস্টেমের কার্য পদ্ধতি :
ইকোসিস্টেমে উদ্ভিদ, প্রাণী ও তাদের পরিবেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত সম্পদ সৃষ্টি ও বিনিময় ঘটছে। এই প্রক্রিয়াকে সম্পদের আবর্তন (ঈুপষরহম ড়ভ সধঃবৎরধষং) বলে। এই আবর্তন প্রক্রিয়ায় সকল শক্তির উৎস সূর্য। একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম। এভাবে সঞ্চিত শক্তি খাদ্য হিসেবে এক জীব থেকে অন্য জীবে স্থানান্তর হয় এবং সেখান থেকে আবার অন্য জীবে স্থানান্তরিত হতে থাকে। প্রতিটি খাদ্য স্থানান্তরের ধাপকে খাদ্য স্তর (ঞৎড়ঢ়যরপ ষবাবষ) বলে। এই স্থানান্তর প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরেই অবশ্য কিছুটা শক্তির অপচয় ঘটে। এই সমগ্র পদ্ধতির নাম শক্তির প্রবাহ (ঋষড়ি ড়ভ বহবৎমু)। ইকোসিস্টেমে জীব ও জড়ের মধ্যে শক্তি প্রবাহ বহমান থাকায় একে গতিশীল বলে মনে করা হয়।
ইকোসিস্টেমের উপাদান :
কার্যপ্রণালির দিক বিবেচনায় ইকোসিস্টেমের উপাদান সম হকে দু’ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এর এক দিকে রয়েছে অটোট্রফিক বা স্বভোজী যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপন্ন করতে সমর্থ, যেমনঃ সবুজ উদ্ভিদ। আবার অন্যদিকে আছে হিটারোট্রফিক বা পরভোজী যারা খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না বলে খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, যেমনঃ মানুষসহ অন্যান্য সকল প্রাণী। কিন্তু গঠনগত দিক বিবেচনায় ইকোসিস্টেমের উপাদানগুলিকে জড় ও জৈবিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।
১। জড় উপাদান:
ইকোসিস্টেমের জড় উপাদানগুলো সাধারণত দু’ধরনের হয়ে থাকে। এর একদিকে রয়েছে মাটি, পানি, খাদ্য, কার্বন—ডাই—অক্সাইড, নাইট্রেজেন, ফসফরাস, প্রভৃতি মৌলিক ও যৌগ দ্রব্যসমূহ এবং অন্যদিকে রয়েছে আলো, তাপ ইত্যাদি শক্তিসমূহ। এগুলি উদ্ভিদ দ্বারা গৃহীত হয় এবং সূর্যালোকের সাহায্যে খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীবের সাহায্যে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ পঁচনের ফলে পুনরায় মাটি ও বায়ুমন্ডলে ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়াকে জীব—ভূ—রাসায়নিক চক্র (ইরড়মবড়পযবসরপধষ পুপষব) বলা হয়। তবে প্রতিটি উপাদানেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং স্থান—কালভেদে পরিবর্তনশীল যা জীবের প্রাচুর্য ও বিস্তৃতিকে প্রভাবিত করে।
২। জৈবিক উপাদান:
পরিবেশের জৈবিক উপাদানসমূহকে চারটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়, এরা হচ্ছে উৎপাদক, খাদক, বিয়োজক ও রূপান্তরক।
(ক) উৎপাদক
এরা সাধারণভাবে নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করতে পারে। এজন্য এদরেকে বলা হয় স্বভোজী (অঁঃড়ঃৎড়ঢ়যং)। সবুজ উদ্ভিদ পত্রস্থ ক্লোরোফিলের সাহায্যে সৌর শক্তিকে পানি ও কার্বন—ডাই—অক্সাইডযোগে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে জৈব খাদ্য উৎপাদন করে। এই খাদ্য উদ্ভিদ নিজে ব্যবহার করে এবং অন্যদের খাদ্যের যোগান দেয়। সবুজ উদ্ভিদ ছাড়াও কিছু কেমোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া এবং বেগুনি রংএর ক্যারোটিনযুক্ত ব্যাকটেরিয়া সূর্যালোক ও যৌগিক পদার্থের উপস্থিতিতে নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে। এজন্য এদেরকেও প্রাথমিক উৎপাদক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
(খ) খাদক
যে সকল জীব নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে না বরং খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল তাদেরকে খাদক বলে। যে সকল প্রাণী একমাত্র উদ্ভিদকেই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে প্রাথমিক খাদক বলে। যেমনঃ ফড়িং, প্রজাপতি, কীট—পতঙ্গ, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, খরগোশ ইত্যাদি। আবার কিছু প্রাণী আছে যারা সরাসরি খাদ্য হিসেবে উদ্ভিদ গ্রহণ না করে তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে। সেইজন্য এদেরকে দ্বিতীয় পর্যায়ের খাদক বা গৌণ খাদক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
যেমনঃ ব্যাঙ, সাপ, কাক, চিল ইত্যাদি প্রাণী। আবার কিছু কিছু মাংসাশী প্রাণী আছে যারা অন্য প্রাণীকতৃর্ক খাদ্যরূপে গৃহীত হয় না। এদেরকে সর্বোচ্চ খাদক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেমনঃ বাঘ, সিংহ, বাজপাখি, কুমির, হাঙ্গর ইত্যাদি। কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা অবশ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়কেই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে থাকে। এদেরকে বলা হয় সর্বভূক প্রাণী, যেমনঃ মানুষ।
(গ) বিয়োজক
যে সকল অণুজীব মৃত জীবদেহে অবস্থিত জৈব পদার্থগুলিকে ধাপে ধাপে ভেঙ্গে সরল পদার্থে রূপান্তরিত করে তাদেরকে বিয়োজক বলে। যে সকল অণুজীব মৃত জীবদেহে অবস্থিত জৈব পদার্থগুলিকে ধাপে ধাপে ভেঙ্গে সরল পদার্থে রূপাš রিত করে তাদেরকে বিয়োজক বলে। ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া বিয়োজকের পর্যায়ভুক্ত। এদের প্রভাবেই প্রাণীদেহের জৈব পদার্থগুলি উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী অজৈব পদার্থে রূপাš রিত হয়। বিয়োজকদেরকে অনেক সময় খাদক হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। কেননা জৈব পদার্থকে সরল পদার্থে পরিণত করার সময় এরা জৈব পদার্থ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে থাকে।

(ঘ) রূপান্তরক
যে সকল ব্যাকটেরিয়া পঁচনের ফলে উৎপন্ন বস্তুর উপর ক্রিয়ার দ্বারা সেগুলিকে জৈব ও অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে তাদেরকে রূপান্তরক বা ট্রান্সফরমার বলে। বিয়োজক ও ট্রান্সফরমারগুলো ইকোসিস্টেমের গতিময়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এদের ক্রিয়া—কর্মের ফলেই জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহ জৈব—ভূ—রাসায়নিক চক্রের মাধ্যমে আদি অবস্থানে ফিরে যায়। অন্যথায়, পৃথিবীর সকল ইকোসিস্টেমই মৃত জৈব উপাদানের আধিক্যে বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেত।
খাদ্য – শিকল
প্রকৃতিতে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে অর্থাৎ তারা স্বভোজী। অন্যসব জীবকে খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপরই নির্ভর করতে হয়। উদ্ভিদ যে খাদ্য তৈরি করে তার কিছু অংশ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করে, বাকি অংশ তার দেহে সঞ্চিত করে রাখে। এই সঞ্চিত খাদ্যই তৃণভোজী প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এভাবে সকল জীব খাদ্য ও খাদক সম্পর্ক স্থাপন করে ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে এবং এর মধ্য দিয়ে উৎপাদক ও সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত খাদ্যের যে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয় তার নাম খাদ্য—শিকল ।

একটি খাদ্য—শিকলে উৎপাদকের সাথে কয়েকটি পর্যন্ত খাদক স্তর থাকতে পারে, তবে সর্বোচ্চ খাদককে কোন প্রাণী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে না। প্রকৃতিতে সাধারণত তিন ধরনের খাদ্য—শিকল দেখা যায়—
(১) শিকারজীবী শিকল :
এই খাদ্য—শিকলে উৎপাদক থেকে প্রথমে ছোট প্রাণী, পরে ক্রমান্বয়ে বড় প্রাণী যুক্ত হয়। যেমনঃ
- ঘাস
- ফড়িং
- ব্যাঙ
- সাপ
(২) পরজীবী শিকল :
এখানে বড় জীব থেকে ক্রমান্বয়ে ছোট জীবের মধ্যে খাদ্য—শিকল গড়ে উঠে, যেমনঃ
- মানুষ
- মশা
- ম্যালেরিয়ার জীবাণু
(৩) মৃতজীবী শিকল :
এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহের উপর ভিত্তি করে খাদ্য—শিকল গড়ে ওঠে, যেমনঃ
- মৃতদেহ
- ছত্রাক
- কেঁচো
খাদ্য – জাল
প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমে খাদ্য—শিকলগুলো সকল সময় সরল পথে চলে না অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে প্রাণীর খাদ্য স্তরের পারস্পরিক বিনিময় ঘটে। যেমনঃ একটি কাক সরাসরি গাছের ফলকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে অথবা তৃণভোজী কীট—পতঙ্গকে খাদ্য হিসেবে বেছে নিতে অথবা কীট—পতঙ্গকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণকারী অন্য কোন প্রাণীকেও তার খাদ্য—সামগ্রীর অšর্Íভূক্ত করতে পারে। এভাবে একটি ইকোসিস্টেমে বিভিন্ন খাদ্য—শিকলের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় ও সংযুক্তির মাধ্যমে যে জটিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার নাম খাদ্য—জাল। সাধারণত খাদ্য—জালে উৎপাদকের সংখ্যা অধিক থাকলেও খাদকের সংখ্যা প্রতিস্তরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে থাকে।

যে কোন ইকোসিস্টেমে প্রাথমিক উৎপাদক প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক, তৃতীয় স্তরের খাদক এবং এভাবে সর্বোচ্চ খাদকের সংখ্যা ভর এবং শক্তির মধ্যে কোন না কোন ভাবে একটি সম্পর্ক বজায় থাকে। খাদ্যস্তরগুলির মধ্যে এই সম্পর্ককে লৈখিক চিত্র অঙ্কন দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব, যা ইকোলোজিক্যাল পিরামিড নামে পরিচিত। ইকোলোজিক্যাল পিরামিডগুলো তিন ধরনের হয়ে থাকে (ক) সংখ্যার পিরামিড, (খ) জীবভরের পিরামিড এবং (গ) শক্তির পিরামিড। সংখ্যা ও জীবভরের পিরামিডের আকৃতি খাড়া বা উল্টানো অথবা অন্য কোন ধরনের হতে পারে, কিন্তু শক্তির পিরামিড সর্বদাই খাড়া আকৃতির হয়ে থাকে।

 ইকোসিস্টেমের গুরুত্ব মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মঙ্গলের জন্যই ইকোসিস্টেম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। সবুজ উদ্ভিদ ঈঙ২, পানি, খাদ্য উপাদান ইত্যাদি ব্যবহার করে সূর্যালোকের সাহায্যে শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য উৎপাদন করছে। এই উৎপাদনের ফলেই উদ্ভিদের আঙ্গিক ও দৈহিক বৃদ্ধি ঘটছে। মানুষসহ সকল প্রাণীর জীবনচক্র চালু রাখার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য হিসেবে উদ্ভিদকর্তৃক উৎপাদিত উপাদানের উপরই নির্ভরশীল হতে হয়। এ কারণেই সব ধরনের ইকোসিস্টেম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা এত তাৎপর্যপূর্ণ।
ইকোসিস্টেমের গুরুত্ব মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মঙ্গলের জন্যই ইকোসিস্টেম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। সবুজ উদ্ভিদ ঈঙ২, পানি, খাদ্য উপাদান ইত্যাদি ব্যবহার করে সূর্যালোকের সাহায্যে শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য উৎপাদন করছে। এই উৎপাদনের ফলেই উদ্ভিদের আঙ্গিক ও দৈহিক বৃদ্ধি ঘটছে। মানুষসহ সকল প্রাণীর জীবনচক্র চালু রাখার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য হিসেবে উদ্ভিদকর্তৃক উৎপাদিত উপাদানের উপরই নির্ভরশীল হতে হয়। এ কারণেই সব ধরনের ইকোসিস্টেম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা এত তাৎপর্যপূর্ণ।