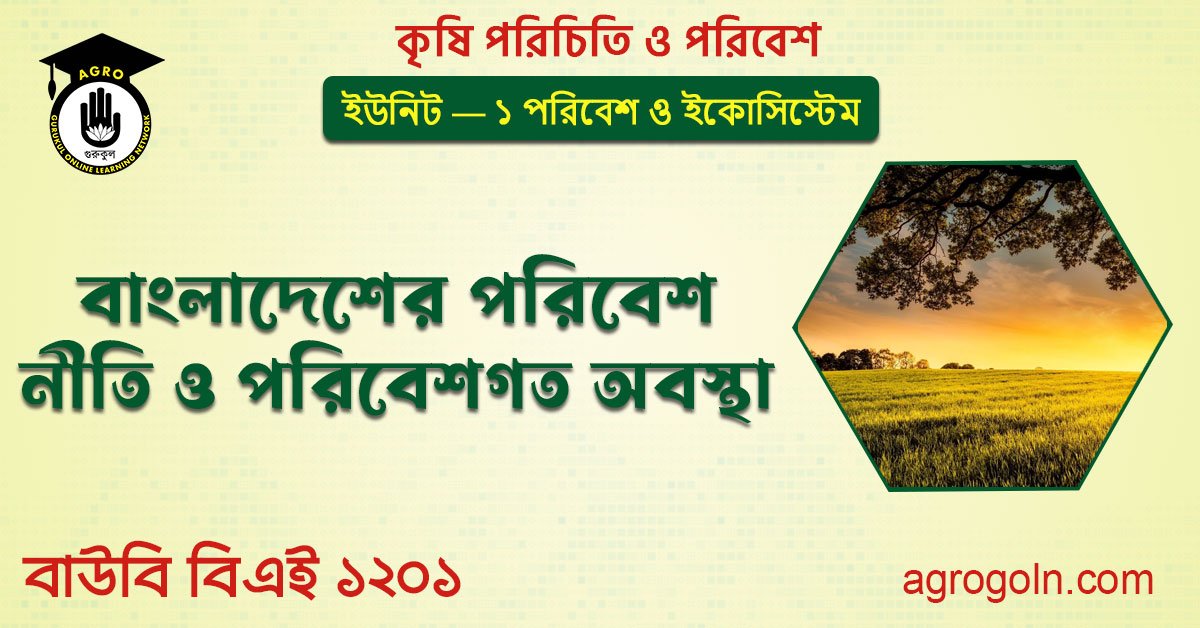বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি ও পরিবেশগত অবস্থা – নিয়ে আজকের আলোচনা। এই পাঠটি “কৃষি পরিচিতি ও পরিবেশ” বিষয়ের “পরিবেশ” বিভাগের ১ নং ইউনিটের ১.৫ নং পাঠ।
Table of Contents
বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি ও পরিবেশগত অবস্থা

পরিবেশ নীতির প্রেক্ষিত আজ বিশ্বজুড়ে পরিবেশ অবক্ষয়ের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। গোটা মানব জাতিকে আসন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য তাই বিশ্বব্যাপী চলছে বিরামহীন প্রচেষ্টা। মানব সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এছাড়া তথ্যের আদান—প্রদান ও ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বহু সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম।
বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের এ ক্রান্তি লগ্নে বাংলাদেশের অবস্থা আরও করুণ। এখানে দেখা দিচ্ছে উপর্যুপরি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার প্রাথমিক লক্ষণাদি ইতোমধ্যেই অনুভূত হচ্ছে। নদ—নদীর নিম্নাংশে লবণাক্ততার প্রকোপ বাড়ছে। ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চলের দ্রুত অবক্ষয়, জলবায়ু ও আবহাওয়ার অস্থিরতাসহ অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যাও বিদ্যমান রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় দেশের পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয় সংক্রান্ত সমস্যাদি চিহ্নিত করে ১৯৯২ সনে পরিবেশ নীতি প্রণয়ন করেছেন।

পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ:
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা।
- দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছোবল থেকে মুক্ত রাখা।
- সব ধরনের দুষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।
- সর্বস্তরে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- সকল জাতীয় সম্পদের লাগসই, দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- পরিবেশসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।
পরিবেশ নীতিমালা
বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কতৃর্ক ১৯৯২ সনে প্রণীত পরিবেশ নীতি সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদত্ত হলো :
বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও তা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান। বন্য প্রাণী ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা ও জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা প্রদান।
১। কৃষি নীতি :
কৃষি উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশসম্মতভাবে করণ। কৃষি সম্পদের ভিত্তি সংরক্ষণ ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। মানুষ ও প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব রাখে এমন সব কৃষি উপকরণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। পরিবেশ অনুকূল প্রাকৃতিক তন্তু যেমন: পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ।
২। শিল্পসংক্রান্ত নীতি :
পরিবেশ দূষণ করে এমন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পস্থাপন নিষিদ্ধকরণ, স্থাপিত শিল্পসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধকরণ এবং এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান কত্তর্ৃক উৎপাদিত পণ্যের পরিবেশ সম্মত বিকল্প পণ্য উদ্ভাবন। প্রচলনের মাধ্যমে ঐ সকল পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ। পরিবেশসম্মত লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ।
৩। স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নীতি :
সকল ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কর্মকান্ড প্রতিরোধ করা। স্বাস্থ্য শিক্ষায় পরিবেশ বিষয়ক কারিকুলাম অন্তভূর্ক্তকরণ। শহর ও গ্রামাঞ্চলে সকলের জন্য পরিবেশসম্মত আবাস ও কর্মস্থলের ব্যবস্থাকরণ।
৪। জ্বালানি নীতি :
পরিবেশ দ ষণকারী জ্বালানিসম হের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ। কম ক্ষতিকারক ও বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ। জ্বালানি সাশ্রয়কারী উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণকরণ। মজুত ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত নতুন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিশ্চিতকরণ।
৫। পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ :
পানি সম্পদ উন্নয়ন ও সেচ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। পানি সম্পদ উন্নয়নে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থার ত্রুটি দুরীকরণ এবং সকল জলাশয়কে দূষণমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ। ভূ—গর্ভস্থ ও ভূ—উপরিস্থ পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানভিত্তিক, টেকসই ও পরিবেশ সম্মতকরণ।
৬। ভূমি ব্যবস্থাপনা :
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা গ্রহণ। ভূমির ক্ষয়রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, ভূমি পুনরূদ্ধার ও বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের সঙ্গে সংঙ্গতিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ। জমির লবণাক্ততা ও ক্ষারীয় প্রভাব রোধকরণ।
৭। বনজ সম্পদ সংক্রান্ত নীতি :
পরিবেশের ভারসাম্য ও আর্থসামাজিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বন ও বৃক্ষাদি সংরক্ষণ এবং নতুন করে বনায়ন। বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও তা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান। বন্য প্রাণী ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা ও জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা প্রদান।
৮। মৎস্য ও পশুসম্পদ :
মৎস্য সম্পদ উন্নয়নকল্পে জলাভূমির সংস্কার ও সংকোচন রোধকরণ। মৎস্য ও পশুসম্পদের উন্নয়ন কর্মসূচীতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য ইকোসিস্টেম যাতেহুমকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিতকরণ। মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পসমূহের পূর্নমূল্যায়ন এবং মাছ চাষের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯। খাদ্য নীতি :
খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বণ্টন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে নিশ্চিতকরণ। বিনষ্ট খাদ্য পরিবেশসম্মতভাবে নিষ্পত্তিকরণ এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানি নিষিদ্ধকরণ।
১০। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ :
উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের পরিবেশসম্মত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং এতদ উপলক্ষে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় সব ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দূষণমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ। সংশিষ্ট এলাকায় মৃত মাছের পরিমাণ সহনশীল মাত্রায় রাখার ব্যবস্থাকরণ।
১১। যোগাযোগ ও পরিবহন :
স্থল, রেল, বিমান ও নৌপথ পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ। অভ্যন্তরীণ নৌ—বন্দর ও ডকইয়ার্ডসমূহ কর্তৃক পানি ও স্থল ভাগের দূষণকার্য নিয়ন্ত্রণকরণ।
১২। গৃহ ও নগরায়ন :
গৃহ ও নগরায়নের সকল পরিকল্পনা ও গবেষনায় পরিবেশগত চিন্তা সম্পৃক্তকরণ। শহর ও গ্রামাঞ্চলের আবাসিক এলাকায় পর্যায়ক্রমে পরিবেশসম্মত সুযোগসুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং নিয়ন্ত্রণ। নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে জলাশয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান।
১৩। জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি :
জনশক্তির সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ এবং বেকার জনশক্তি ব্যবহার উৎসাহিতকরণ।
১৪। শিক্ষা ও গণ—সচেতনতা :
দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষিতের হার দ্রূত বৃদ্ধিকরণ। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যাপারে ব্যাপক গণ—সচেতনতা সৃষ্টিকরণ। প্রাতিষ্ঠানিক ও অ—প্রাতিষ্ঠানিক সকল শিক্ষা কার্যক্রমে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় অন্তভূর্ক্তকরণ।সরকারী, বেসরকারী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পরিবেশসংক্রান্ত বিষয় অন্তভূক্তর্করণ।
১৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ দষণ তদারক ও নিয়ূ ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরোপকরণ। জাতীয় সম্পদের লাগসই, দীর্ঘস্থায়ী এবং পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ।
বাংলাদেশের পরিবেশগত অবস্থা কোন দেশের পরিবেশগত অবস্থা নির্ভর করে তার ভৌগলিক অবস্থান, আবহাওয়ার তারতম্য, বনজসম্পদের পরিমাণ, মাটির প্রকৃতি, আর্থ—সামাজিক অবস্থান, জনসংখ্যা, শিক্ষার হার, শিল্পের অগ্রসরতা ইত্যাদির উপর। তবে বাংলাদেশের পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে :
১। জনসংখ্যার আধিক্য:
প্রায় এক লক্ষ চুয়ালিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান। এর জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১২ কোটি এবং বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ২.১ ভাগ। সীমিত জায়গায় বিপুল জনগোষ্ঠীর অবস্থান, তাদের দারিদ্র ও অশিক্ষা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের পরিবেশের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।
২। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ:
বাংলাদেশ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা প্রভৃতি নদী বিধৌত পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব—দ্বীপ দেশ। উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সীমিত পাহাড়িয়া উচ্চভূমি বাদে পুরো দেশটাই এক বিশাল সমভূমি। দেশের মাঝ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এ দেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলভুক্ত। তবে সাগর সান্নিধ্য হওয়ায় এবং মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা প্রকট নয়। মানব সৃষ্ট কারণ ছাড়াও বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বাংলাদেশের পরিবেশ আর যেসব কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হচ্ছে :
বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট অধিকাংশ ঘ ূর্ণিঝড়ই বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে। বাংলাদেশে বিশেষ ধরনের মোচাকৃতির উপকূল রেখা থাকার কারণেই এমনটি হয়ে থাকে।
(ক) ঘূর্ণিঝড় :
বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড়ই বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে। বাংলাদেশে বিশেষ ধরনের মোচাকৃতির উপকূল রেখা থাকার কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কারণে প্রচুর প্রাণহানি ও সম্পদের অবক্ষয় ঘটে। আবাদি জমিতে লোনা পানি ঢুকে উর্বরতা বিনষ্ট করে, ফলে স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়।
(খ) বন্যা :
পদ্মা, মেঘনা, যমুনাসহ ছোট বড় বহু নদী বাংলাদেশের উপর দিয়ে বহমান। প্রায় সবগুলি নদীরই উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশের বাইরে। বর্ষা মৌসুমে এসব নদী প্রচুর পানি ও পলি বহন করে মাঠ ঘাট ছাপিয়ে তুলে। এর সাথে যোগ হয় মৌসুমী বৃষ্টিপাত। ফলে সমভূমিতে দেখা দেয় বন্যা। মৌসুমভেদে বন্যার প্রকোপ খুবই তীব্রতর হয়। ফলে ভেসে যায় মাঠ, ঘাট, শহর, বন্দর, এবং গ্রাম—জনপদ। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটে মাঠ ফসলের এবং বাড়ি ঘরের। প্রাণহানি ঘটে মানুষ, গবাদিপশু ও অন্যান্য প্রাণীর। দূষিত হয়ে পড়ে পানিসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদান। ফলে প্রাদুর্ভাব ঘটে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়সহ প্রাণঘাতী বহু রোগের।
(গ) কালবৈশাখী ও টর্নেডো :
প্রতিবছরই চৈত্র—বৈশাখ মাসে রদ্ররোষে আঘাত হানে ূ কালবৈশাখী। মৌসুমী—পূর্ব ঋতুর এমন ঝড়োবাতাস প্রধানত উত্তর পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এই ঝড়ের সর্বোচ্চ বেগ ৬০ থেকে ১৩০ কি. মি. এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই ঝড়ের সাথে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং কখনো কখনো বজ্রসহ শিলা বৃষ্টিপাত ঘটে। কালবৈশাখীর বজ্র—মেঘ কখনো কখনো শক্তি সঞ্চয় করে মারাত্বক আকার ধারণ করে এবং হাতির শুঁড়ের আকৃতি সদৃশ মেঘ ভূমির দিকে নেমে আসে।
এর নাম টর্নেডো। স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন স্থানের বায়ুর চাপ দ্রুত কমে ২৫ মিলিবারের নিচে নেমে আসলে ভয়াবহ টর্নেডোর আশঙ্কা থাকে। টর্নেডোর শুঁড়ের আওতায় থাকে প্রচন্ড ঘূর্ণি। যে এলাকার উপর দিয়ে এ ঝড় প্রবাহিত হয় সেখানে ঘরবাড়ি, গাছ—পালা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। প্রাণ হারায় অসংখ্য প্রাণী। অনেক সময় মাঠের ফসল পর্যন্ত জ্বলে পুড়ে যায়।

৩। জ্বালানি ও বনসম্পদ
দ্রূত গতিতে বাড়ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন বাসস্থান, আসবাবপত্র, জ্বালানি ইত্যাদি উপকরণ। আর এসবের সিংহ ভাগই আসছে বনসম্পদ থেকে। ফলে দেশের সীমিত বনসম্পদের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৬ শতাংশ। সুতরাং বন উজাড়িকরণের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে । ভূমি ক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছে, নদীর ভাঙ্গন ও বৃদ্ধি পাচ্ছে । প্রভাব পড়ছে আবহাওয়ার উপর বাড়ছে ঝড় জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা। আবাসস্থল সংকুচিত হওয়ায় বিপন্নের মুখোমুখি বহু বন্যপ্রাণী।
৪। অপরিকল্পিত নগরায়ন
দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ শহরাঞ্চলে বাস করে। বৃহৎ শহরগুলির মধ্যে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ৬০ লক্ষের উপরে এবং আগামী ২০০০ সালের মধ্যে হয়ত ১ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ শহরাঞ্চলে বাস করে। বৃহৎ শহরগুলির মধ্যে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ৬০ লক্ষের উপরে এবং আগামী ২০০০ সালের মধ্যে হয়ত ১ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। অন্যান্য বড় শহরগুলির জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
এই বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য যে নাগরিক সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন ছোট বড় কোন শহরেই তা পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেনি। শহরগুলিতে রয়েছে আয়তনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত আবাস গৃহ, সংকীর্ণ রাস্তা—ঘাট, ত্রুটিপূর্ণ পয়:প্রণালী ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা, যত্রতত্র বস্তি এলাকা এবং আরও বহুবিধ সমস্যা। ফলে শহরের বাসিন্দারা প্রায়ই শ্বাসযন্ত্রের রোগ, যক্ষ্মা, কৃমি, ডাইরিয়া, আমাশয়, হেপাটাইটিস, এবং টাইফয়েডের মতো অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও দুষিত পানি সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।
৫। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন
বাংলাদেশ শিল্পোন্নত দেশ নয়। তথাপি ছোট বড় বেশ কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান এখানে রয়েছে এবং নতুনভাবে গড়ে উঠছে। ভারী শিল্পের মধ্যে রয়েছে পাট, বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সিমেণ্ট, সার এবং জাহাজ নির্মাণ। মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে চামড়া, খাদ্য, তামাক, গার্মেণ্টস, ডিস্টিলারি শিল্পের নাম উলেখযোগ্য। অধিকাংশ শিল্প কারখানাগুলোর অবস্থান শিল্প এলাকার বাইরে, যেমন নদ—নদীর ধারে অথবা কোন আবাসিক এলাকায়। এসকল শিল্প কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পরিশোধনের কোন্ ব্যবস্থা নেই। ফলে তা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ।