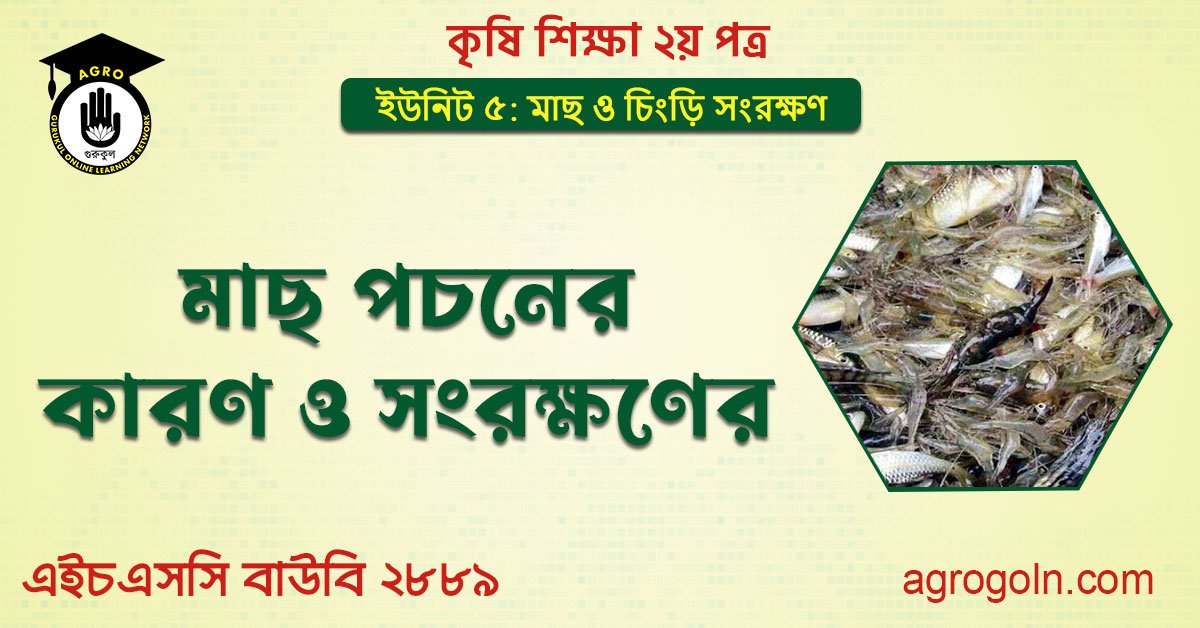বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। দেশের বিস্তীর্ণ নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল মাছ উৎপাদনের এক অপার সম্ভাবনার উৎস। মাছ আমাদের খাদ্যচাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস। তবে মাছ একটি দ্রুত পঁচনশীল পণ্য হওয়ায় আহরণের পরপরই যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে তা খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন মূল্যবান সম্পদের অপচয় ঘটে, তেমনি ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়।
তাই মাছের পঁচন প্রতিরোধ ও দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য প্রাচীন কালের নানান indigenous (দেশজ) পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। এ পাঠে আমরা মাছ পঁচনের কারণ, এর লক্ষণ এবং বিভিন্ন সংরক্ষণ কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানবো, যা আমাদের মাছের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও কৃষি অর্থনীতিকে টেকসই করতে সহায়তা করবে।
Table of Contents
মাছ পঁচনের কারণ ও সংরক্ষণ
পাঠ ৫.১: মাছ পঁচনের কারণ ও সংরক্ষণ
(কৃষি শিক্ষা ২য় পত্র | ৫ম ইউনিট)
মাছ পঁচনের কারণ:
মাছ একটি অত্যন্ত পচনশীল খাদ্যপণ্য। আহরণের পরপরই যদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা হয়, তাহলে মাছ দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। মাছ পঁচে যাওয়ার ফলে এর গুণগতমান ও পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়, এবং বাজারজাত করাও কঠিন হয়ে পড়ে। মাছ পঁচনের প্রধান তিনটি কারণ নিচে আলোচনা করা হলো:
১. মাছের দেহের অভ্যন্তরের এনজাইমের ক্রিয়া
মাছের দেহে স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন এনজাইম থাকে, যা জীবিত অবস্থায় হজম ও কোষ গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু মাছ মারা গেলে এই এনজাইমগুলো কোষ ও কলাকে ভেঙে ফেলতে থাকে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় অটোলাইসিস। এর ফলে মাছের স্বাদ নষ্ট হয়, পেশি নরম হয়ে পড়ে, চোখ দেবে যায় এবং দেহের রং পরিবর্তিত হয়।
২. অণুজীবের সংক্রমণ ও বিক্রিয়া
মাছের ত্বক, আইশ, ফুলকা ও নাড়িভুঁড়িতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুদ্র অণুজীব থাকে। জীবিত অবস্থায় এগুলো ক্ষতিকর নয়, কিন্তু মাছ মারা গেলে পরিবেশ, মানুষের হাত, সংরক্ষণ ও পরিবহণ পাত্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত জীবাণু সংক্রমণ ঘটে। এসব জীবাণু মাছের দেহে এনজাইম নিঃসরণ করে এবং তা দ্রুত পঁচন শুরু করে।
৩. রাসায়নিক বিক্রিয়া
মাছের দেহে আমিষ, স্নেহ (চর্বি) ও জলীয় উপাদান বেশি পরিমাণে থাকে। বিশেষ করে মাছের চর্বিতে থাকা অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্ষতিকর রাসায়নিক তৈরি করে। এর ফলে মাছের কোষ ও কলা নষ্ট হয় এবং পঁচে যেতে শুরু করে।
মাছ একটি সংবেদনশীল পণ্য হওয়ায় মাছ আহরণের পর থেকেই সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা জরুরি। কারণ, মাছ একবার পঁচে গেলে তা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না। সংরক্ষণের সময় সামান্য অবহেলাতেও মাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাছ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো—
- মাছের গুণগতমান অক্ষুণ্ণ রাখা,
- অণুজীবের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা,
- অণুজীবের বৃদ্ধি ব্যাহত করা,
- মাছের পানি অপসারণ ও
- অণুজীব ধ্বংস করা।
চিংড়ি একটি উচ্চমূল্যের মৎস্যজাত পণ্য এবং খুবই দ্রুত পঁচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। চিংড়ি আহরণের সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর চিংড়ি আহরণ করা হয়। এর মধ্যে বড় আকারের চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করা হয়, কিন্তু ছোট আকারের চিংড়ি কম দামে বিক্রি হয় এবং সহজে পঁচে যায়।
চিংড়ি সংরক্ষণের মাধ্যমে—
- এর গুণগতমান বজায় রাখা যায়,
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়,
- এবং বিশাল পরিমাণ পচনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
বাংলাদেশে সাধারণত কাঠ বা বাঁশের তৈরি ঝুড়িতে বরফ দিয়ে চিংড়ি সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও বরফসহ চাটাই বা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দ্রুত প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পাঠানো হয়।
মাছ ও চিংড়ি পঁচন রোধে সময়মতো ও সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাছ পঁচনের কারণগুলি বুঝে ব্যবস্থা নিলে উৎপাদিত মাছ ও চিংড়ির মান রক্ষা করে খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।
মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি :
মাছ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। সকল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল মাছের গুণগত মান ঠিক রাখা। বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণের কারণে সংরক্ষিত মাছে গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ, ও বাহ্যিক গঠনে কিছুটা পরিবর্তন হয়।
মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর নাম নিম্নে দেওয়া হলো :
ক. বরফজাতকরণ বা আইসিং ।
খ. লবণজাতকরণ বা সল্টিং ।
গ. শুটকিকরণ বা ড্রাইং ।
ঘ. হিমায়িতকরণ বা ফ্রিজিং।
ঙ. টিনজাতকরণ বা ক্যানিং।
চ. ধূমায়িতকরণ বা স্মোকিং ।
ক. বরফজাতকরণ বা আইসিং পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ:
বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতিকে বরফজাতকরণ বা আইসিং বলা হয়। এটি মাছ সংরক্ষণের একটি স্বল্পমেয়াদি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে মাছের দেহের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস (০°C) বা তার কাছাকাছি নামিয়ে আনা হয়। এতে অণুজীবের বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার ব্যাহত হয় এবং মাছ পঁচে যাওয়া রোধ করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে সাধারণত ব্লক আইস ভেঙে গুঁড়া আকারে ব্যবহার করে মাছ সংরক্ষণ করা হয়।
বরফজাতকরণের সুবিধা
বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা রয়েছে, যেমন:
১. যেকোনো মৌসুমে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।
২. এটি সহজ ও কার্যকর একটি সংরক্ষণ পদ্ধতি।
৩. বরফ বাংলাদেশে সহজলভ্য।
৪. যেকোনো আকারের মাছ এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণযোগ্য।
৫. বরফ ক্ষতিকর নয় এবং খুব দ্রুত মাছকে ঠান্ডা করে পঁচন রোধ করে।
৬. বরফজাত মাছ সহজে পরিবহন করা যায়।
বাংলাদেশে প্রচলিত বরফজাতকরণ পদ্ধতি
বাংলাদেশে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথমে মাছকে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়। এরপর বাঁশের চাটাই বা মাদুর দিয়ে তৈরি ঝুড়িতে স্তরে স্তরে বরফ ও মাছ সাজিয়ে রাখা হয়। সাধারণত ৪ ভাগ মাছের সঙ্গে ১ ভাগ বরফ মেশানো হয়, তবে পরিবহন দূরত্ব ও সময়ের ভিত্তিতে বরফের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।
বড় আকারের বরফ ব্লক গুঁড়া করে ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট অনুপাতে বরফ ও মাছ পাত্রে রাখার পর তা চট বা মাদুর দিয়ে ঢেকে সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং কাঠের বাক্সে পরিবহন করা হয়। সঠিক অনুপাত ও উপযুক্ত পাত্র ব্যবহারের মাধ্যমে মাছকে ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।
বরফজাতকরণের অসুবিধা
বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের কিছু সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা রয়েছে, যেমন:
১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে বরফ তৈরিতে অপরিষ্কার পানি ব্যবহৃত হয়, যা মাছের জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়।
২. তাপ কুপরিবাহী (insulated) পাত্র ব্যবহার না করলে বরফ দীর্ঘ সময় কার্যকর থাকে না।
৩. বড় আকারের বরফ টুকরা মাছের শরীর ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
৪. বরফ ও মাছের অনুপাতে ভুল হলে মাছের পুষ্টিগুণ নষ্ট হতে পারে।
৫. অপরিষ্কার পাত্র ব্যবহারে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।
অসুবিধাগুলোর প্রতিকার ও করণীয়
বরফজাতকরণে বিরাজমান ত্রুটি ও মাছের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করা উচিত:
১. সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই সতেজ ও টাটকা মাছ বেছে নিতে হবে।
২. একই আকার ও একই প্রজাতির মাছ একই পাত্রে রাখতে হবে।
৩. বরফ তৈরির জন্য পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে।
৪. বড় মাছ হলে নাড়িভুঁড়ি অপসারণ করে সংরক্ষণ করতে হবে।
৫. বরফ ও মাছের অনুপাত শীতকালে ১:২ এবং সাধারণভাবে ১:১ রাখা উত্তম।
৬. সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত পাত্র ও সরঞ্জাম সবসময় পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
৭. পাত্রে মাছ ও বরফ এমনভাবে রাখতে হবে যাতে গলিত পানি, রক্ত ও ময়লা নিচে চুইয়ে পড়ে এবং মাছ পরিষ্কার থাকে।
৮. সংরক্ষণের সময় পাত্রে প্রথমে এক স্তর বরফ, এরপর মাছ, এবং সবশেষে আবার বরফের স্তর দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হবে।

খ. লবণজাতকরণ বা সল্টিং পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ:
লবণজাতকরণ মাছ সংরক্ষণের একটি সহজ, কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মাছের দেহে লবণ প্রবেশ করানো হয়, যা অভিশ্রবণ (osmosis) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাছের কোষ থেকে পানি বের করে দেয়। ফলে মাছের দেহে লবণের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং জীবাণুর (অণুজীব) বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার বাধাগ্রস্ত হয়। এতে মাছ দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত থাকে।
লবণজাতকরণের ফলে মাছের গঠন, রং ও গন্ধে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসে। সাধারণত চর্বিযুক্ত মাছ এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণযোগ্য।
✅ লবণজাতকরণের সুবিধাসমূহ
১. স্বল্প খরচে সংরক্ষণ:
লবণজাতকরণ একটি তুলনামূলকভাবে কম খরচের সংরক্ষণ পদ্ধতি।
২. দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ:
এই পদ্ধতিতে মাছ দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখা সম্ভব।
৩. সহজ প্রক্রিয়া:
লবণজাতকরণ একটি সহজ ও সহজলভ্য পদ্ধতি, যা অল্প প্রশিক্ষণেই কার্যকরভাবে করা যায়।
৪. উপকরণ সহজলভ্য:
বাংলাদেশে লবণ সস্তা এবং সহজেই পাওয়া যায়, যা এই পদ্ধতির একটি বড় সুবিধা।
৫. পরিবহণযোগ্যতা:
লবণজাতকৃত মাছ সহজে ও নিরাপদে দূর দূরান্তে পরিবহণ করা যায়।
লবণজাতকরণের প্রকারভেদ:
লবণজাতকরণ প্রধানত তিন ধরনের হতে পারে:
১. শুষ্ক লবণজাতকরণ (Dry Salting)
এই পদ্ধতিতে মাছকে ধুয়ে কেটে নেওয়ার পর মাছের ওপরে ও ফাঁকে ফাঁকে দানাদার লবণ ছিটিয়ে বা মেখে রাখা হয়। মাছ ও লবণ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়। এই পদ্ধতি সহজ ও প্রচলিত।
২. আর্দ্র লবণজাতকরণ (Wet Salting or Brining)
এ পদ্ধতিতে মাছকে একটি লবণ দ্রবণে (Brine solution) ডুবিয়ে রাখা হয়। এতে লবণ মাছের দেহে প্রবেশ করে এবং পানি বেরিয়ে আসে। তবে পানি বের হওয়ায় লবণ দ্রবণের ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে, তাই দ্রবণ মাঝে মাঝে পরিবর্তন বা ঘন করতে হয়।
৩. মিশ্র লবণজাতকরণ (Mixed Salting)
এটি একটি উন্নততর পদ্ধতি। প্রথমে মাছকে শুষ্ক লবণের মাধ্যমে লবণায়িত করা হয় এবং পরে লবণ দ্রবণে রাখা হয়। এভাবে সংরক্ষণ করলে লবণজাতকরণ অধিক কার্যকর হয় এবং মাছ দীর্ঘদিন ভালো থাকে।
বাংলাদেশে মাছ লবণায়নে বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহ :
বাংলাদেশে মাছ সংরক্ষণের জন্য সাধারণত শুষ্ক দানাদার লবণ ব্যবহৃত হয়। এখানে মাছ লবণায়নের দুটি প্রধান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়:
১. শুষ্ক লবণায়ন পদ্ধতি
২. ভিজা লবণায়ন পদ্ধতি
| ধরণ | ধাপ/বিবরণ | বিশদ |
| ১. শুষ্ক লবণায়ন | ড্রেসিং | মাছের আঁশ, পাখনা, নাড়িভুঁড়ি ফেলে বুক থেকে পিঠ পর্যন্ত আড়াআড়ি কেটে টুকরো করা হয় (পিছনে সংযুক্ত থাকে)। |
| লবণের অনুপ্রবেশ | মাছের ভিতরে ও বাইরে লবণ ঘষে দেওয়া হয়। চোখ ও ফুলকায়ও লবণ ঢোকানো হয়। লবণ ও মাছের অনুপাত ১:৪। | |
| রাইপেনিং | লবণ-মাখানো মাছ ঝুড়িতে স্তরে স্তরে সাজানো হয়, প্রতি স্তরের নিচে লবণ থাকে। ঝুড়ি খড়ের মাদুরে ঢেকে ছায়ায় রাখা হয়। সময় লাগে ৭–১০ দিন। | |
| গুদামজাতকরণ | রাইপেনিং শেষে টিনের পাত্রে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। | |
| ২. ভিজা লবণায়ন | ড্রেসিং | মাছের মাথা কেটে ফেলা হয়। মাছকে তীর্যকভাবে কেটে খোলা অংশ বাড়ানো হয়। |
| লবণ মাখানো ও সংরক্ষণ | মাছে শুষ্ক লবণ মাখিয়ে, টিনের পাত্রে ফাঁকা রেখে সাজানো হয়। অভিশ্রবণে বের হওয়া পানি ফাঁকা স্থানে জমা হয়। | |
| উপকারিতা | এই পদ্ধতিতে গুণগত মান ভালো থাকে এবং দীর্ঘদিন সংরক্ষণযোগ্য। | |
| ৩. ইলিশ মাছের বিশেষ পদ্ধতি | কারণ | চর্বিযুক্ত হওয়ায় শুঁটকি করা যায় না, হিমায়ন ব্যয়বহুল, বরফায়ন স্বল্পমেয়াদি— তাই লবণায়ন কার্যকর। |
| প্রক্রিয়া | আঁশ, নাড়িভুঁড়ি ফেলে ১/২ ইঞ্চি করে কাটা হয়। মাছের ওজনের ১৫–২৫% লবণ ঘষে দেওয়া হয়। | |
| রাইপেনিং ও সংরক্ষণ | লবণ মেশানো টুকরো ঝুড়ি/পাটাতনে স্তরে স্তরে রাখা হয়। নিচে লবণের আস্তরণ থাকে, উপর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। রাইপেনিং সময় ৫–৭ দিন। |
বাংলাদেশে ইলিশ মাছ লবণজাতকরণের সুবিধা /অসুবিধা:
| 🔷 বিষয় | ✅ সুবিধা | ❌ অসুবিধা |
| ১. সংরক্ষণযোগ্যতা | চর্বিযুক্ত হওয়ায় শুঁটকি করা না গেলেও লবণায়ন সহজে করা যায়। | পচা বা বাসি মাছ লবণায়নের জন্য ব্যবহৃত হলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। |
| ২. প্রক্রিয়ার সহজতা | পদ্ধতিটি সহজ ও জেলেদের কাছে পরিচিত। | লবণায়নের সময় স্বাস্থ্যবিধি সাধারণত মানা হয় না। |
| ৩. পুষ্টিগুণ | লবণজাত মাছের পুষ্টিমান অনেকাংশে অপরিবর্তিত থাকে। | অতিরিক্ত লবণ ব্যবহারে প্রোটিন ডিন্যাচারেশন ঘটে যেতে পারে। |
| ৪. উপকরণ | লবণ সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় সহজে প্রয়োগযোগ্য। | অনেক সময় অপরিষ্কার লবণ ব্যবহৃত হয়, যা গুণগত মান নষ্ট করে। |
| ৫. অনুপাত ও মান | (—) | নির্দিষ্ট লবণ-মাছ অনুপাত না থাকায় সংরক্ষণের মান ঠিক থাকে না। |
| ৬. ড্রেসিং ও পরিষ্কার | (—) | অনেক সময় মাছ ভালোভাবে ড্রেসিং বা ধোয়া হয় না, এতে মান নষ্ট হয়। |
| ৭. সংরক্ষণের পরিবেশ | (—) | খোলা জায়গায় সংরক্ষণে চর্বি জারণ হয়ে মাছের গন্ধ ও গুণমান খারাপ হয়। |
গ. শুটকিকরণ বা ড্রাইং পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ:
শুঁটকিকরণ হলো প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সূর্যালোক ও বাতাসের সাহায্যে মাছ থেকে পানি বা জলীয় অংশ হ্রাস করে মাছ সংরক্ষণ করার পদ্ধতি। সাধারণত মাছের দেহে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ পানি থাকে। মাছ ধরা হওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ রাখা হলে মাছ পচন শুরু হয়। সূর্যালোকে মাছ শুকানো হলে মাছের পচন রোধ হয়। বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতি হলো এই শুঁটকিকরণ।
শুঁটকিকরণের উদ্দেশ্য
১. মাছের পুষ্টিমান বজায় রাখা।
২. মাছ সংরক্ষণের খরচ কমিয়ে সহজে গুদামজাতকরণ সম্ভব করা।
৩. উৎপাদনকে বাণিজ্যিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও পুষ্টিগুণের দিক থেকে মানসম্মত করা।
৪. স্বল্প পরিশ্রমে সহজে মাছ সংরক্ষণ করা।
শুঁটকিকরণ পদ্ধতি
বাংলাদেশে সাধারণত শীতকালীন মৌসুমে সূর্যালোকের সাহায্যে মাছ শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। এই সময় আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত কম থাকে এবং সূর্যালোকের স্থায়িত্বও বেশি থাকে, যা শুঁটকিকরণের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ জেলা এসব এলাকার প্রধান শুঁটকি উৎপাদন কেন্দ্র। এসব অঞ্চলে হাওড়-বাঁওড়, বিল ও উপকূলীয় এলাকা থেকে প্রচুর মাছ ধরা হয়।
শুঁটকিকরণে ছোট ও বড় উভয় প্রকার মাছ ব্যবহৃত হয়।
- ছোট মাছ: চান্দা, পুঁটি, মলা, ঢেলা, টেংরা ইত্যাদি।
- বড় মাছ: শোল, গজার, বোয়াল, টাকি, লইট্টা, ছুটি, কোরাল, ফলিচান্দা, রূপচান্দা ইত্যাদি।
ছোট মাছ শুঁটকিকরণ পদ্ধতি
ছোট মাছ যেমন চান্দা, মলা, ঢেলা, পুঁটি, টেংরা ইত্যাদি সূর্যালোকে শুকানো হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত মাছের আঁশ, নাড়িভুঁড়ি ও পাখনা ফেলা হয় না। কখনো কখনো শুকানোর পূর্বে মাছগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। মাছগুলো চাটাই বা মাদুরের উপর বিছিয়ে রোদে শুকানো হয়। সাধারণত ৩-৫ দিনের মধ্যে শুঁটকিকরণ সম্পন্ন হয়।
বাংলাদেশে শীতকালে প্রচুর মাছ ধরা হয়। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে সব মাছ বাজারজাত করা সম্ভব হয় না। অনেক মাছ কম দামে বিক্রি বা পচে যায়। তাই সূর্যালোকের সাহায্যে শুঁটকিকরণ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শুঁটকিকরণের গুরুত্ব:
১. অর্থনৈতিক গুরুত্ব:
বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মাছের অবদান অসাধারণ। যদিও মৎস্যজীবীরা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারেন না, প্রাকৃতিক শুঁটকিকরণ পদ্ধতিতে কম খরচে মাছ সংরক্ষণ করা যায়।
২. জেলেদের কাছে গ্রহণযোগ্য:
এই পদ্ধতি জেলেদের মধ্যে সহজলভ্য এবং বহুল পরিচিত।
৩. সহজ পদ্ধতি:
শুঁটকিকরণ তুলনামূলকভাবে খুব সহজ ও কার্যকর।
৪. গুণগত মান বজায় থাকে:
শুঁটকিকৃত মাছের পুষ্টিমান ও গুণগত মান তাজা মাছের কাছাকাছি থাকে।
৫. দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ:
শুঁটকিকরণের মাধ্যমে মাছ অনেকদিন সংরক্ষিত রাখা যায়, যা বাজারে মাছের অভাবের সময় সঠিক পরিমাণ সরবরাহ নিশ্চিত করে।
৬. আবহাওয়া উপযোগী:
বাংলাদেশের শীতকালীন আবহাওয়া ও সূর্যালোক শুঁটকিকরণের জন্য আদর্শ।
উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে শুঁটকিকরণের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটি দেশের মৎস্য সংরক্ষণ ও অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।
শুঁটকিকরণের সময় সতর্কতা
শুঁটকির সময় মাছ বিভিন্ন ধরনের অণুজীব, পোকামাকড়, পাখি ও কীটপতঙ্গের আক্রমণের শিকার হতে পারে। এ থেকে রক্ষা পেতে পলিথিন সীট বা জালের ব্যবহার উপকারী। দ্রুত শুষ্ক করার জন্য মাঝে মাঝে মাছ উল্টে দেয়া হয়।
বড় মাছ শুঁটকিকরণ পদ্ধতি :
বাংলাদেশে যে বড় মাছগুলো শুঁটকিকরণ করা হয়, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো— শোল, গজার, বোয়াল, লইট্টা, ছুরি ইত্যাদি। বড় মাছ শুঁটকিকরণের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপ:
ক. মাছ বাছাই:
শুঁটকিকরণের জন্য তাজা ও টাটকা মাছ বাছাই করা অত্যন্ত জরুরি। এতে উচ্চমানের শুঁটকি তৈরী সম্ভব হয়।
খ. পরিষ্কারকরণ:
প্রথমে মাছের আঁশ, পাখনা, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি অংশ ফেলে দিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
গ. মাছ কাটা:
মাছকে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত মেরুদণ্ড বরাবর কাটা হয়, তবে লেজের দিকে সামান্য অংশ সংযুক্ত থাকে। এই অংশের সাহায্যে শুকানোর সময় মাছ ঝুলিয়ে রাখা যায়। এই কাটা অংশগুলোকে ফিলেট বলা হয়।
ঘ. ফিলেট কাটা:
প্রতিটি ফিলেটের মাঝ বরাবর ছুরি দিয়ে ২-৩ বার কাটা হয়, যা দ্রুত শুষ্ক হওয়ার জন্য সাহায্য করে।
ঙ. শুকানো:
মাছগুলোকে পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ৭-৮ দিন শুকানোর প্রয়োজন হয়।
চ. জলীয় অংশ:
শুঁটকি মাছের জলীয় অংশ সাধারণত ১০-২০% থাকে।
শুঁটকি মাছ শুকানোর পর মাদুর বা কুঁড়েঘরে সংরক্ষণ করা হয়। পরে মাটির পাত্র বা মটকায় রাখা হয়, যেখানে অভ্যন্তরে মাছের তেল মাখানো থাকে যাতে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতি শুঁটকিকরণের অসুবিধা :
বাংলাদেশে প্রচলিত শুঁটকিকরণ পদ্ধতিতে বেশ কিছু সমস্যা বিদ্যমান, যা মাছের গুণগত মান ও স্বাস্থ্যকরতা প্রভাবিত করে। প্রধান অসুবিধাগুলো হলো—
১. আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীলতা:
শুঁটকিকরণ সম্পূর্ণরূপে আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। আর্দ্রতা বেশি থাকলে মাছ শুষ্ক হতে বেশি সময় লাগে।
২. স্বাস্থ্যবিধির অভাব:
কর্মরত ব্যক্তিরা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ না করলে শুঁটকি রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৩. কঠিন শুঁটকি:
শুঁটকির গঠন কখনো বেশি শক্ত হয়ে যায়, যা রান্নায় অসুবিধার কারণ হয়।
৪. পোকামাকড়ের আক্রমণ:
উন্মুক্ত স্থানে শুকানোর কারণে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় ও তাদের লার্ভা শুঁটকিতে আক্রমণ করতে পারে।
৫. কালো বর্ণের শুঁটকি:
অনেক সময় শুঁটকির রং কালো হয়, যা বাজারে চাহিদা কমায়।
৬. অতিরিক্ত তেল প্রয়োগ:
শুঁটকিকে উজ্জ্বল করার জন্য তেল দিয়ে ব্রাশ করলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।
৭. পচা মাছ ব্যবহারের সম্ভাবনা:
কখনো কখনো পচা বা বাসি মাছ শুঁটকিকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা গুণগত মান নষ্ট করে।
৮. ত্রুটিপূর্ণ গুদামজাতকরণ:
অবৈজ্ঞানিক ও ভুল পদ্ধতিতে শুঁটকি সংরক্ষণ করলে তার গুণগত মান হ্রাস পায়।
শুঁটকিকরণের অসুবিধা দূরীকরণের উপায় :
শুঁটকির গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখতে ও সংক্রমণ রোধ করতে নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা উচিত—
১. টাটকা মাছ ব্যবহার:
শুঁটকিকরণের জন্য অবশ্যই টাটকা মাছ বাছাই করতে হবে। অধিক চর্বিযুক্ত মাছ শুঁটকিকরণে ব্যবহার না করাই উত্তম।
২. স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা:
শুঁটকিকরণে নিয়োজিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিষ্কারের জন্য ক্লোরিনযুক্ত পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. সতর্কতার সঙ্গে অংশ ছেঁটে ফেলা:
মাছের নাড়িভুঁড়ি, পাখনা, আঁশ যথাযথভাবে সরাতে হবে, যেন মাংসের অংশে কোন ক্ষতি না হয়।
৪. মাছ ধৌতকরণ:
ড্রেসিং শেষে মাছ ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে ২-৫% লবণীয় পানিতে ৫ মিনিটের জন্য ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে যাতে প্রাথমিক সংক্রমণ কমে।
৫. উচ্চ স্থান ও নিরাপদ স্থানে শুকানো:
মাছ মাটিতে বা বালতিতে না রেখে মাচা বা চাটাইয়ের ওপর শুকানো উচিত। দ্রুত শুকানোর জন্য এবং পোকামাকড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শুকানোর সময় জাল ব্যবহার করতে হবে।
৬. বায়ু-নিরোধক পাত্রে সংরক্ষণ:
খোলা জায়গায় শুঁটকি সংরক্ষণ না করে বায়ু নিরোধক পাত্রে রাখা উচিত। ছোট পরিমাণের জন্য পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে, বড় পরিমাণের জন্য টিনের পাত্র ভালো। পাত্রের অভ্যন্তরে জীবাণু রোধক এন্টি-অক্সিডেন্ট যেমন ই-টোকোফেরল ব্যবহার করা যেতে পারে।
ঘ. হিমায়িতকরণ বা ফ্রিজিং পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ:
হিমায়িতকরণ মাছ সংরক্ষণের একটি উন্নতমানের ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মাছের তাপমাত্রা এমনভাবে কমিয়ে আনা হয় যাতে মাছের দেহের পানিকে সম্পূর্ণ বরফে পরিণত করা যায়। ফলে মাছের কোষের ভেতরের জলীয় অংশ জমে যায় এবং অণুজীবের বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে মাছের গুণগত মান দীর্ঘ সময় ধরে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সংরক্ষণের সময় এক বছর পর্যন্ত হতে পারে।
বাংলাদেশে বিশেষ করে চিংড়ি ও অন্যান্য মূল্যবান মৎস্যজাত সামগ্রী হিমায়িতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। হিমায়িতকরণ পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকারের হয়— দ্রুত হিমায়ন এবং ধীর হিমায়ন, যার মধ্যে ধীর হিমায়ন সবচেয়ে উন্নত ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত।
হিমায়িতকরণ পদ্ধতির ধাপসমূহ:
১. প্রাথমিক প্রস্তুতি:
বড় আকারের মাছ বরফজাতকরণের পূর্বে মাছ থেকে নাড়ি, ভুঁড়ি, মাথা ও পাখনা পরিষ্কার করে ফেলা হয়। এরপর ঠাণ্ডা পানিতে মাছগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া হয়।
২. চিংড়ির প্রক্রিয়াজনকরণ:
চিংড়ির ক্ষেত্রে সাধারণত মাথা ছেঁটে ফেলা হয় এবং সাইজ অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।
৩. ক্লোরিন পানিতে ডুবানো:
মাছ ও চিংড়িকে ২০% থেকে ৮০% ক্লোরিনযুক্ত পানিতে নির্দিষ্ট সময় ডুবিয়ে রাখা হয়, যা জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে এবং মাছের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৪. টুকরো করা:
প্রয়োজন অনুসারে মাছ ও চিংড়িকে ধারালো ছুরির সাহায্যে টুকরা টুকরা করে কাটা হয়, যাতে হিমায়ন প্রক্রিয়া আরও দ্রুত এবং কার্যকর হয়।
৫. সোডিয়াম ট্রাইফসফেট ব্যবহার:
কাটাকাটা মাছ ও চিংড়ি ১০-১২% সোডিয়াম ট্রাইফসফেট দ্রবণে ১০ মিনিটের জন্য ডুবিয়ে রাখা হয়। এটি মাছের রং ও স্বাদ বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং হিমায়িত অবস্থায় মাছের গুণগত মান রক্ষা করে।
৬. হিমায়িতকরণ:
প্রক্রিয়াজাত মাছ ও চিংড়িকে দ্রুত শীতলীকরণ করে হিমায়িত করা হয়, যা মাছের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করে।
হিমায়িতকরণের গুরুত্ব:
- দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ: মাছের গুণগত মান দীর্ঘ সময় ধরে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়।
- রপ্তানির জন্য আদর্শ: আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের মাছ ও চিংড়ির মান বৃদ্ধি পায়।
- সংক্রমণ রোধ: জীবাণু বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় স্বাস্থ্যকর পণ্য নিশ্চিত হয়।
- তাজা স্বাদ ও পুষ্টি: মাছের স্বাদ, রং ও পুষ্টিগুণ অপরিবর্তিত থাকে।
ঙ. টিনজাতকরণ বা ক্যানিং পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ:
টিনজাতকরণ পদ্ধতি হলো খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে মাছ বা মাংসজাতীয় খাদ্য সংরক্ষণের আধুনিক ও কার্যকরী একটি পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রতিটি ধাপ খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখা ও দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে টিনজাতকরণের ধাপগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো—
১. কাঁচামাল নির্বাচন
টিনজাতকরণের জন্য টাটকা ও মাংসল চর্বিযুক্ত মাছ বা মাংসকে বেছে নেয়া হয়। কাঁচামালের গুণগত মান টিনজাত খাদ্যের স্বাদ ও পুষ্টিমানে প্রভাব ফেলে।
২. টিন বা কৌটা পূরণ
টিনজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রধানত টিন বা ধাতব পাত্র (কৌটা) ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে অ্যালুমিনিয়াম বা কাচের পাত্রও ব্যবহৃত হতে পারে। টিনে খাদ্য ভর্তি করার সময় পাত্রের উপরের অংশ সামান্য ফাঁকা রাখা হয় যাতে নিষ্ক্রিয় গ্যাস দিয়ে ফাঁকা অংশ পূরণ করা যায়, যা খাদ্যকে অক্সিজেন থেকে রক্ষা করে।
৩. উপাদান সংযোজন
খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও রঙ বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন উপাদান যেমন—গ্লুটামেট, তেল, টমেটো সস, মসলা ইত্যাদি যোগ করা হয়। এর ফলে টিনজাত খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও পুষ্টিমানের উন্নতি ঘটে।
৪. বায়ুশূন্যকরণ ও কৌটাবদ্ধকরণ
টিনজাত খাদ্যের অক্সিডেশন রোধ এবং পাত্রের স্ফীতি বা ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য কৌটা থেকে বায়ু শূন্য করে দেয় এবং পরে সিল করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য দীর্ঘদিন সুস্থ থাকতে পারে।
৫. ধৌতকরণ
সিলকরণের পর টিনের বাইরে থাকা ময়লা ও খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ধৌত করে পরিষ্কার করা হয়, যাতে প্যাকেজিংয়ের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে।
৬. প্রক্রিয়াকরণ ও উত্তপ্তকরণ
জীবাণুমুক্ত করার জন্য উচ্চতাপে কৌটাভুক্ত খাদ্য উত্তপ্ত করা হয়। সাধারণত ১২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৫ পাউন্ড চাপ দিয়ে ৩০ মিনিট উত্তপ্তকরণ সম্পন্ন হয়, যা খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
৭. ঠাণ্ডাকরণ
উত্তপ্ত করার পর খাদ্যের তাপমাত্রা দ্রুত কমাতে ঠাণ্ডা বায়ু বা ঠাণ্ডা পানির সাহায্য নেওয়া হয়। এটি খাদ্যের দুর্গন্ধ দূর করে এবং গুণগত মান রক্ষা করে।
৮. লেবেলিং
ঠাণ্ডাকরণের পর কৌটার উপর খাদ্যের নাম, উৎপাদন কোম্পানির তথ্য, পুষ্টি উপাদান, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি সঠিকভাবে লেবেল করা হয়, যা ভোক্তাদের জন্য তথ্যবহুল ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
৯. গুদামজাতকরণ
প্রস্তুতকৃত টিনজাত খাদ্য সরাসরি বাজারজাত না করে নির্দিষ্ট সময় গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। এই গুদামজাতকরণের মাধ্যমে খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ এবং পুষ্টিমানের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়।
টিনজাতকরণ পদ্ধতি খাদ্য সংরক্ষণে আধুনিক ও নিরাপদ পদ্ধতি হওয়ায় এটি আজকের সময়ের খাদ্যশিল্পে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সঠিক নিয়মে টিনজাত খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করলে খাদ্যের দীর্ঘায়ু ও পুষ্টিমান অটুট থাকে।
চ. ধূমায়িতকরণ বা স্মোকিং পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ:
ধূমায়িতকরণ বা স্মোকিং পদ্ধতি একটি স্বল্পমেয়াদী মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি, যা কাঠ পোড়ানোর সময় উৎপন্ন ধোঁয়া এবং তাপের যৌথ প্রভাবে মাছের দেহ থেকে আর্দ্রতা অপসারণ করে মাছকে সংরক্ষিত রাখে। এই পদ্ধতিতে মাছের স্বাদ, রং ও গন্ধে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন আসে, যা খাদ্যতালিকায় এর গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে। যদিও ধূমায়িতকরণ দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত নয়, তবুও এটি দ্রুত এবং সহজে মাছ সংরক্ষণের একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
ধূমায়িতকরণের প্রক্রিয়া ও উপকরণ
- কাঁচামাল নির্বাচন:
সাধারণত পরিপক্ব ও চর্বিযুক্ত মাছ ধূমায়িতকরণের জন্য উপযুক্ত। বড় আকারের মাছকে ফিলেটে কাটতে হয়, যেখানে ছোট মাছ সাধারণত পুরো করেই ধূমায়িত করা হয়। - প্রস্তুতি ও লবণায়ন:
মাছকে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক (মোল্ড) বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সুরক্ষিত রাখতে ৬০-৭০% লবণ সমৃদ্ধ দ্রবণে প্রায় ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মাছের পেশীতে প্রায় ২-৩% লবণ প্রবেশ করে, যা সংরক্ষণে সহায়ক। - ধূমায়ন:
কাঠ পোড়ানোর মাধ্যমে উৎপন্ন ধোঁয়া এবং তাপের সাহায্যে মাছের আর্দ্রতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয়। ধোঁয়ার রসায়ন মাছের পৃষ্ঠে প্রলেপ গঠন করে, যা ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণুর বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। - সংরক্ষণ:
ধূমায়িত মাছ সাধারণত কাঠের বাক্স বা অন্যান্য উপযুক্ত পাত্রে প্যাক করা হয়। এই পদ্ধতিতে মাছকে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করা সম্ভব।
ধূমায়িতকরণের সুবিধা
- মাছের স্বাদ ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়, যা ভোক্তাদের কাছে জনপ্রিয়।
- দ্রুত এবং সহজ পদ্ধতি হওয়ায় ছোট ও মাঝারি পরিমাণে মাছ সংরক্ষণের জন্য উপযোগী।
- ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- মাছের আর্দ্রতা কমে যাওয়ায় ওজন কমে, ফলে পরিবহণে সুবিধা হয়।
সীমাবদ্ধতা
- দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত নয়; সংরক্ষণ সময় সীমিত (২-৩ সপ্তাহ)।
- ধূমায়িত মাছের গন্ধ ও স্বাদ সবাই পছন্দ নাও করতে পারে।
- পর্যাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত ধূমায়ন প্রক্রিয়া না হলে মাছের গুণগত মান নষ্ট হতে পারে।
মাছ একটি পচনশীল খাদ্যশস্য, যার পচনের কারণ প্রধানত মাছের অভ্যন্তরীণ এনজাইমের কার্যক্রম, ক্ষুদ্র জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়ার প্রভাব এবং দেহের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকে। মাছ আহরণের পর যত দ্রুত সম্ভব উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে মাছ দ্রুত পচে যায় এবং এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই মাছ সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে মাছের গুণগত মান অক্ষুণ্ন থাকে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন বরফজাতকরণ, লবণজাতকরণ, শুঁটকিকরণ এবং ধূমায়িতকরণ প্রায় প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব পদ্ধতির সঠিক ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রয়োগ মাছের পচন রোধে সহায়ক এবং বাজারজাতকরণের সময়কাল বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রচলিত এসব পদ্ধতি মাছের পুষ্টিমান ধরে রেখে জেলেদের আয় বৃদ্ধিতে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
অতএব, মাছ পঁচন থেকে রক্ষা করতে সময়োপযোগী, পরিচ্ছন্ন ও বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে মাছের অপচয় কমানো সম্ভব এবং ভোক্তাদের কাছে মানসম্মত ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।