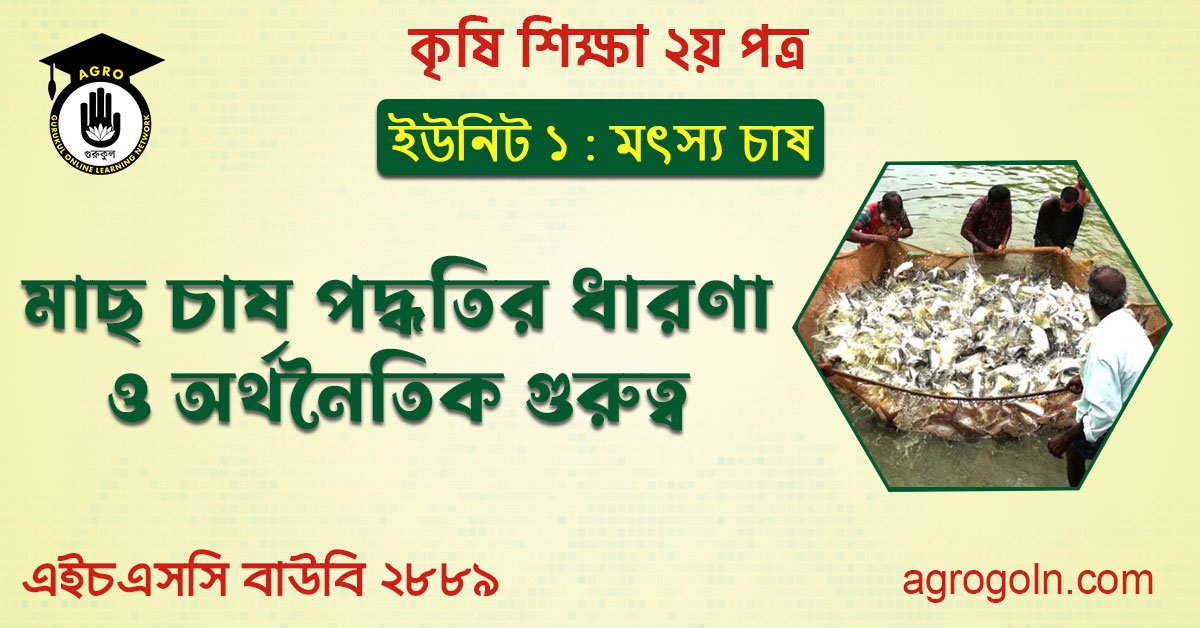মৎস্য চাষ ও মাছ চাষ পদ্ধতির ধারণা – কৃষি পরিচিতি ও পরিবেশ বিষয়ের একটি পাঠ। এই পাঠটি ১ নং ইউনিটের ১.৪ নং পাঠ। মৎস্য চাষ ও মাছ চাষ পদ্ধতির ধারণা বাংলাদেশে মাছ চাষের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। তবে নাজির আহমেদ (১৯৪৭—১৯৬০) নতুনভাবে এদেশে মাছ চাষের গোড়া পত্তন করেন। স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প পরিশ্রমে প্রচুর মাছ উৎপাদন এবং মাছের ব্যবসা হতে আর্থিক আয়ের বিরাট সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় কালক্রমে এ অঞ্চলে পুকুরে মাছ চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। দেশে বর্তমানে মাছের চাষ পদ্ধতিতে বেশ উন্নতি সাধিত হলেও এখনও বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প হিসেবে এটি গড়ে ওঠেনি।
মৎস্য চাষের গুরুত্ব
মৎস্য বা মাছ বলতে শীতল রক্ত বিশিষ্ট (ectothermic= cold blooded) জলজ মেরুদন্ডী প্রাণিকে বোঝায় যারা অভ্যন্তরিন ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালনা করে এবং জোড় বা বিজোড় পাখনার সাহায্যে পানিতে চলাচল করে। তবে সব মাছই যে শীতল রক্তবিশিষ্ট এমনটি ভাবার অবকাশ নেই। কিছু মাছ আছে যেমন—White shark এবং Tuna মাছ তাদের দেহের তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে। অর্থাৎ পরিবেশের তাপমাত্রার তারতম্যের সাথে তাদের দেহের তাপমাত্রার তারতম্য হয় না।
Fish Base এর তথ্য মতে অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত পৃথিবীতে ৩৩,৪০০ প্রজাতির কথা জানা যায়। তবে অনেক প্রজাতি আছে যাদের সস্পর্কে এখনও বর্ণনা করা হয়নি অথবা এখনও অজানা। জানা মাছের প্রজাতির সংখ্যাটি মেরুদন্ডী প্রাণির অন্যান্য সকল শ্রেণীর (স্তন্যপায়ী, উভচর, সরীসৃপ ও পাখী) সম্মিলিত যোগফলের চাইতেও বেশী।
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যখন আমরা মাছ বা মৎস্য বলি তখন শুধুমাত্র মাছকেই বোঝানো হয়। আর যখন মাৎস্য বলি তখন মাছের সাথে সাথে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন সকল জলজ প্রাণীকে বোঝায়।
জীববিজ্ঞানের যে শাখায় মাছের বিভিন্ন দিক যেমন— শ্রেনীবিন্যাস, মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা, মাছের প্রজনন, প্রতিপালন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বিপণন, রোগতত্ত্ব তথা মাছ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে মৎস্যবিজ্ঞান বলে। বর্তমানে মাছ চাষের সাথে অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলজ প্রাণি যেমন— চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, কচ্ছপ, ব্যাঙ ইত্যাদি চাষ করা হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় মাছ চাষকে বলা হয় একোয়াকালচার (Aquaculture)।
Aquaculture শব্দটি Latin শব্দ Aqua’ যার অর্থ “পানি” এবং English শব্দ ‘culture’ যার অর্থ “চাষ” নামক দু’টি শব্দের সমম্বয়ে গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ Aquaculture অর্থ পানিতে চাষ অথবা মাছ চাষ। অন্যভাবে, নিয়ন্ত্রিত বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলজ জীবের চাষকে একোয়াকালচার বলে। একে অয়ঁধভধৎসরহম ও বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ: মাছ চাষ (Fish farming/culture), চিংড়ি চাষ (Shrimp farming/culture), ওয়েস্টার চাষ (Oyster farming/culture), সীউঈড চাষ (Seaweed farming/culture) ইত্যাদি।
মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic improtance of fish culture) :
পরিবেশিক ও প্রাকৃতিক কারণে মৎস্য চাষে বাংলাদেশ বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। “মাছে ভাতে বাঙালি”— প্রবাদ বাক্যটি বাংলাদেশের মৎস্য ঐতিহ্যেরই ইঙ্গিত বহন করে। মাছ এদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। পুষ্টিমান উন্নয়ন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার্জন, আর্থ—সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাছ চাষের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।
(১) পুষ্টিমান উন্নয়ন:
পুষ্টিগত দৃষ্টিকোন থেকে দেহগঠনে আমিষের ভূমিকা ব্যাপক। তুলনামূলক বিচারে প্রাণিজ আমিষ দেহের জন্য ভালো উচ্চ মূল্যের কারণে এদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দৈনন্দিন খাবারের সাথে প্রাণিজ আমিষ বিশেষ করে গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির মাংসের সংস্থান করতে পারে না। এই শ্রেণির মানুষের পুষ্টিমান উন্নয়নে মৎস্য আমিষের ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য।
সস্তায় পওয়া যায় এমন মাছ খেয়ে এদের দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা মিটে। শুধু এরাই নয়, এদেশের প্রায় সব শ্রেনির সব মানুষের কাছেই মাছ সমানভাবে প্রিয়। সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশের মানুষ দৈনিক যে পরিমান প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করে তার প্রায় ৬০% ই আসে মাছ এবং চিংড়ি থেকে। গুণগত মানে অন্যান্য আমিষের চেয়ে মৎস্য আমিষ ভালো।
পর্যাপ্ত পরিমান মাছ খেলে মানুষের বুদ্ধিমত্তা বাড়ে, রোগের ঝঁুকি কমে এবং সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়। মিঠা ও লোনা পানির মাছে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায় যা মানুষের শরীরের জন্য বেশ উপকারি। এছাড়া আয়রণ ও জিংকের ভালো উৎস হলো ছোট মাছ। কাজেই মানুষের দৈনিক খাবারের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ খাওয়া উচিত। ২০১৫—১৬ অর্থবছরে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, এদেশের মানুষের দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমান ৬০ গ্রামে উন্নীতকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
(২) কর্মসংস্থান সৃষ্টি:
দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক বা ১ কোটি ৮৫ লক্ষ লোক হ্যাচারি পরিচালনা, মৎস্য চাষ, মৎস্য আহরণ, বিক্রি, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজের সাথে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। এসব কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে প্রায় ১৫ লক্ষ নারী মৎস্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত। সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্য সেক্টরে বেকার পুরুষ ও নারীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
এক্ষেত্রে প্রচলিত হ্যাচারির ব্যবহার আধুনিকায়ন করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদা—মাফিক মানসম্পন্ন পোনার উৎপাদন ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করত: সম্ভাব্য সকল জলাশয়কে আধুনিক চাষ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। একই সাথে উৎপাদিত মৎস্য বিপণন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে করে মাছের গুণগত মান ঠিক থাকে এবং মাছ ও মাছজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এসকল ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বেকার নর—নারীদেরকে খাতওয়ারী প্রশিক্ষণের আওতায় এনে দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
(৩) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন:
স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দিনে দিনে এ সেক্টরের অবদান ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বলছে মৎস্য খাতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় দেশ।কাজেই, এখাতের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।
(৪) আর্থ:
সামাজিক উন্নয়ন: বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে অসংখ্য পুকুর ডোবা ছড়িয়ে আছে। এসব পুকুরের সিংহভাগ মাছ চাষের আওতায় আনা হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও পতিত। পতিত বা আপাত মাছ চাষ অযোগ্য এসব পুকুরের মালিকানা দেশের প্রান্তিক চাষী বা বিত্তহীনদের হাতে। সংস্কারের মাধ্যমে এ সমস্ত পুকুরে মাছ চাষ করে বিত্তহীন লোক এবং বেকার যুবকদের আর্থ—সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।
(৫) হাঁস:
মুরগির খাদ্য:
বাংলাদেশে হাঁস—মুরগির চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।
সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে এদের খাদ্যের চাহিদা। মাছের অব্যবহৃত অংশ যেমন—আঁইশ, কাটা, নাড়িভঁুড়ি ইত্যাদি এবং ফিসমিল (ঋরংযসবধষ) দ্বারা হাঁস—মুরগির জন্য উত্তম সুষম খাদ্য তৈরী করা সম্ভব। এসব আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য হাঁস—মুরগিকে খাওয়ালে ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
(৬) পতিত জমির সদ্ব্যবহার:
পতিত/অব্যবহৃত জমিতে পুকুর খনন করে মাছ চাষ করলে পারিবারিক মাছের চাহিদা মেটানোর সাথে সাথে আর্থিকভাবেও কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে।
কাজেই উপরের আলোচনা থেকে এটা বলা যায় যে, বাংলাদেশে মাছ চাষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।