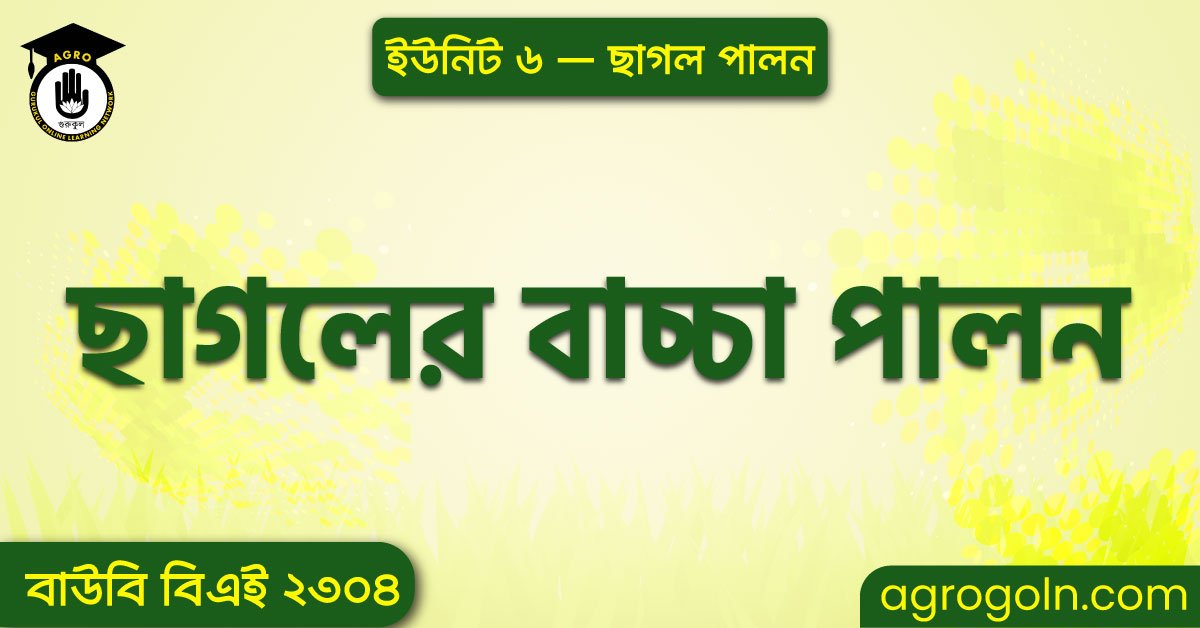আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-ছাগলের বাচ্চা পালন।
এই পাঠ শেষে আপনি-
- কীভাবে নবজাত ছাগলের বাচ্চার যত্ন নিতে হয় তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- শালদুধ কী তা লিখতে পারবেন।
- বাচ্চা ছাগলের পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বাচ্চা ছাগলের দুধ ছাড়ানোর সঠিক সময় বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বাচ্চা ছাগল ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
ছাগলের বাচ্চা পালন
নবজাত বাচ্চা ছাগলের (newborn kid) সঠিক যত্নের ওপরই এদের বেড়ে ওঠা ও ভবিষ্যৎ উৎপাদন নির্ভর করে। নবজাত বাচ্চার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না বলে এরা অত্যন্ত রোগ সংবেদনশীল হয়। এমতাবস্থায় সামান্য যত্নের অভাবে বাচ্চার মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই সুস্থ সবল বাচ্চা পেতে হলে যেমন গর্ভাবস্থায় ছাগীর সুষ্ঠু যত্ন ও পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি প্রসবকালীন ও নবজাত বাচ্চার যত্ন নেয়া আবশ্যক। প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলে গর্ভবর্তী ছাগীকে বিশেষ নজরে রাখতে হবে এবং কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণত কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই বাচ্চা প্রসব হয়। তবে গর্ভস্থ বাচ্চার বা ছাগীর জননতন্ত্রের অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রসবকালে বিঘ্ন ঘটে। এমতাবস্থায় নিজে টানাটানি করে বাচ্চা প্রসব করানো ঠিক নয়। বরং সঙ্গে সঙ্গে পশু চিকিৎসক বা ভেটেরিনারি সার্জনের (Veterinary Surgeon) শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ছাগী সাধারণত একাধিক বাচ্চা প্রসব করে। প্রথম বাচ্চা প্রসবের ১৫-২০ মিনিট পর সাধারণত দ্বিতীয় এবং একই সময় অন্তর পরবর্তী বাচ্চা প্রসব করে। তাই প্রথম বাচ্চা প্রসবের পর তেমন ব্যস্ত তার প্রয়োজন হয় না। জন্মের সময় পুরুষ বাচ্চা গুলো সাধারণত ওজনে স্পী বাচ্চা গুলোর থেকে বড় হয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা গুলো জন্মের সময় গড়ে প্রায় এক কিলোগ্রাম হয়ে থাকে
নবজাত বাচ্চা ছাগলের যত্ন
নিম্নলিখিতভাবে নবজাত বাচ্চা ছাগলের যত্ন নিতে হয়-
১) বাচ্চার শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করা :
বাচ্চা প্রসবের পরপরই বাচ্চার নাক ও মুখের লালা (saliva) এবং শ্লেষ্মা (mucus) পরিষ্কার করে দিতে হবে। নতুবা শ্বাস বন্ধ হয়ে বাচ্চার মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। বাচ্চা জন্ম নেয়ার পর শ্বাসপ্রশ্বাস না নিলে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে বাচ্চার
জিহ্বায় সুড়সুড়ি বা নাড়াচাড়া দিলে কাশি দিতে চাইবে যা শ্বাসতন্ত্র কে কার্যকরী করতে সাহায্য করবে। তাছাড়া বাচ্চার বুকের পাঁজরের হাড়ে আস্তে আস্তে বার কয়েক চাপ দিলেও শ্বাসপ্রশ্বাস চালু হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও বাচ্চার নাক-মুখে ফুঁ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করা যায়।
২) বাচ্চার শরীর পরিষ্কার করা ও শুকানো :
প্রসবের পর ছাগী তার বাচ্চার শরীর, মুখ প্রভৃতি জিহ্বা দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দেয়। প্রথম প্রসবের ক্ষেত্রে অনেক সময় ছাগী বাচ্চার গা চাটে না। এক্ষেত্রে বাচ্চার গায়ে একটু লবণ ছড়িয়ে দিলেই চাটতে থাকবে।
এতেও কাজ না হলে পরিষ্কার কাপড়, চট বা নরম খড় দিয়ে বাচ্চার পুরো শরীর ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করে দিতে হবে। কোনোক্রমেই নবজাত বাচ্চার শরীর পানি দিয়ে ধোয়া যাবে না। এতে ঠান্ডা লেগে বাচ্চা মারা যেতে পারে। শীতে বাঅতিরিক্ত ঠান্ডায় শুকনো কাপড় বা চট দিয়ে বাচ্চাকে ঢেকে দিতে হবে। এছাড়াও আগুন জ্বেলে বাচ্চার শরীর গরম রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৩) বাচ্চার নাভি রজ্জু (Navel cord) কাটা :
বাচ্চার নাভি রজ্জু দেহ থেকে ২.৫-৫.০ সে.মি. বাড়তি রেখে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে হবে। কাটার পর উক্ত স্থানে টিঙ্কচার আয়োডিন বা টিঙ্কচার বেনজয়িন নামক জীবাণুনাশক ওষুধ লাগাতে হবে। ফলে নাভি রজ্জু দিয়ে দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারবে না। নাভী রজ্জু বেধে না দেয়াই ভালো।
৪) বাচ্চাকে শালদুধ বা কলস্ট্রাম (Colostrum) পান করানো :
জন্মের পর কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত বাচ্চার কোনো খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। সুস্থ সবল বাচ্চা জন্মের ১৫-২০ মিনিট পর থেকেই দাঁড়ানোর চেষ্টা করে এবং প্রথম দুধ অর্থাৎ শালদুধ বা কলস্ট্রাম পান করতে সক্ষম হয়। বাচ্চার জন্মের ১-২ ঘণ্টার মধ্যেই এ দুধ পান করানো উচিত। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ দুধ পান করাতে হবে। যদি দুর্বলতার কারণে বাচ্চা। দাঁড়াতে বা দুধ পান করতে না পারে তবে ছাগী থেকে দুধ দোহন করে তা বোতলে ভরে চুষির (nipple) সাহায্যে পান করাতে হবে।
অনুশীলন (Activity) : ধরুন, আপনার খামারে একটি ছাগী বাচ্চা দিয়েছে। কীভাবে নবজাত বাচ্চাটির যত্ন নিবেন তা ধারাবাহিকভাবে লিখুন ।
শালদুধ বা কলস্ট্রাম কী
বাচ্চা জন্মের পর ছাগী থেকে প্রথম যে দুধ পাওয়া যায় তা শালদুধ বা কলস্ট্রাম নামে পরিচিত। নবজাত বাচ্চার প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুধ জন্মের দিন থেকে অন্তত ৩-৪ দিন বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে পান করাতে হবে। শালদুধের রঙ হলুদ এবং এই দুধ আঠালোviseous) হয়।
গরম করলে কলস্ট্রাম জমাট বেধে যায়। স্বাভাবিক দুধের তুলনায় শালদুধে ৩-৫ গুণ বেশি আমিষ থাকে। এই আমিষের অধিকাংশই গ্লোবিউলিন (globulin) নামক আমিষ যা রোগপ্রতিরোধী অ্যান্টিবডিসমৃদ্ধ (antibody)। নবজাত বাচ্চার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শালদুধ এদেরকে রোগের কবল থেকে রক্ষা করে।
স্বাভাবিক দুধের থেকে শালদুধে ৫-১৫ গুণ বেশি ভিটামিন-এ থাকে। বাচ্চার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজপদার্থগুলোও এই দুধে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। শালদুধ কোষ্ঠ পরিষ্কারক (laxative), তাই নবজাত বাচ্চার পরিপাকতন্ত্রে যে হলুদ বর্ণের বিপাকজাত মল জমে থাকে তা বের করে দিয়ে খাদ্য অন্ত কে পরিষ্কার করে। নবজাত বাচ্চা কোনো কারণে মাতৃহারা হলে সাধারণ দুধের সঙ্গে ডিমের সাদা অংশ বা অ্যালরুমেন (albumen), এক চামচ কড লিভার তেল (cod liver oil) ও এক চামচ পানি মিশিয়ে বিকল্প বা কৃত্রিম কলস্ট্রাম তৈরি করে পান করানো যায়।
বাচ্চা পালন পদ্ধতি
দু’টো পদ্ধতিতে ছাগলের বাচ্চা পালন করা হয়। যথা- ১. প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মায়ের সঙ্গে রেখে ও ২. কৃত্রিম পদ্ধতিতে মা থেকে পৃথক অবস্থায় হাতে পালন (artificial rearing)। প্রতিটি পদ্ধতিরই কিছু কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। তবে, এদেশে প্রাকৃতিক পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে বাচ্চাকে মায়ের সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হয়।
ফলে বাচ্চা নিজের ইছে এবং প্রয়োজনমতো মায়ের কাছ থেকে দুধ পান করতে পারে। কৃত্রিমভাবে মা থেকে পৃথক অবস্থায় হাতে পালনের ক্ষেত্রে দু’টো পদ্ধতি প্রচলিত। একটি পদ্ধতিতে বোতলের মাধ্যমে (bottle feeding) এবং অন্যটিতে বালতির মাধ্যমে (pan feeding) বাচ্চাদের দুধ পান করানো হয়।
বাচ্চারা সহজেই এসব পদ্ধতিতে দুধ পানে অভ্যস্ত হয়ে যায়। দুপদ্ধতির মধ্যে বোতল পদ্ধতিটিই অপেক্ষাকৃত ভালো ও সুবিধাজনক। কারণ, বাচ্চা বোতলের নিপল চুষে দুধ পান করলে তাদের মস্তিষ্কে এক ধরনের উদ্দীপনার (stimulation) সৃষ্টি হয়। এতে সহজেই লালা (saliva) তৈরি হয় যা দুধ হজমে সাহায্য করে। অনেক সময় শিশু অবস্থায় মা মারা গেলে ধাত্রী মায়ের (foster mother) দুধ পান করানোর পদ্ধতিও এদেশে প্রচলিত আছে।
মা থেকে বাচ্চা আলাদা করা
মা ছাগল থেকে বাচ্চা আলাদা করা নির্ভর করে কোন্ উদ্দেশ্যে ছাগল পালন করা হচ্ছে তার ওপর। যেমন- মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হলে বাচ্চাকে বেশি দিন পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করাতে হবে। আমাদের মতো গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশে সাধারণত ৩ মাস বয়সের পূর্বে এই ধরনের বাচ্চা ছাগল মা থেকে আলাদা করা ঠিক নয়। তবে, যেসব ছাগল বেশি দুধ দেয় তাদের ক্ষেত্রে বাচ্চাকে ৩-৪ দিন কলস্ট্রামসমৃদ্ধ দুধ পান করানোর পর আলাদা করে নেয়া যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে বোতল দিয়ে দুধ পানের অভ্যাস করাতে হবে।
বাচ্চা ছাগল ব্যবস্থাপনা
সাধারণত দু’সপ্তাহ বয়স থেকেই বাচ্চারা কাঁচা ঘাস বা লতাপাতা খেতে আরম্ভ করে। তাই এদের নাগালের মধ্যে কিছু কিছু কচি ঘাস, লতাপাতা এবং দানাদার খাদ্য রাখতে হয়। এতে এরা আস্তে আস্তে কঠিন খাদ্য খেতে অভ্যস্ত হয়। এসময় বাচ্চাদের জন্য প্রচুর উন্মুক্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা গাছের নিচে পরিমাণমতো জায়গায় বেড়া দিয়ে বাচ্চা পালন করা যায় । এতে এরা একদিকে পর্যাপ্ত ছায়া পেতে পারে। অন্যদিকে, দৌড়াদৌড়ি এবং ব্যয়াম করারও প্রচুর সুযোগ পায় যা তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অত্যন্ত দরকারী। প্রতিটি বাচ্চা ছাগলকে জন্মের প্রথম সপ্তাহে দৈনিক ৩০০-৩২৫ মি.লি. দুধ ৩-৪ বারে পান করাতে হবে। ধীরে ধীরে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৬-৭ সপ্তাহে তা ৭৫০-৮৫০ মি.লি.-এ উন্নীত করতে হবে।
দুধের বিকল্প খাদ্য ৩ সপ্তাহ বয়সের পর খেতে দেয়া যেতে পারে। ৩ সপ্তাহ থেকে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে দিনে দুবেলা দুধ বা দুধের বিকল্প খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। ১০-১১ সপ্তাহে দৈনিক দুধ সরবরাহের পরিমাণ ২০০-১০০ মি.লি. নামিয়ে আনতে হবে।
এসময় দৈনিক ৩০০-৩৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য ও প্রচুর কচি ঘাস, লতাপাতা সরবরাহ করতে হবে। ৩-৪ মাস বয়সে দুধ পান করানো পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ, এসময় বাচ্চা বড় হয়ে যায় এবং কঠিন খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার জন্য এদের পাকস্থলী পুরোপুরিভাবে তৈরি হয়ে যায়।
প্রজননের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্য না থাকলে ২-৩ মাস বয়সেই পুরুষ বাচ্চাগুলোকে খাসি করে দিতে হবে। কারণ, এটা প্রমাণিত সত্য যে, খাসি করলে মাংসের গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। অন্যথায় এদেরকে স্পী বাচ্চার (doe kid) কাছ থেকে আলাদা করে পালন করতে হবে ।
শরৎ ও হেমন্ত কালে ছাগলের মৃত্যুহার অত্যধিক বেশি থাকে। এসময় কৃমির আক্রমণ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া নিউমোনিয়া (Pneumonia) এবং এন্টারোটক্সিমিয়া (Enterotoxaemia) ব্যাপক হারে দেখা দিতে পারে। তাই এসময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বাচ্চার বয়স দু’সপ্তাহ হলে প্রথম বার এবং দু’মাস পূর্ণ হলে দ্বিতীয় বার নির্ধারিত মাত্রায় কৃমির ওষুধ সেবন করাতে হবে ।