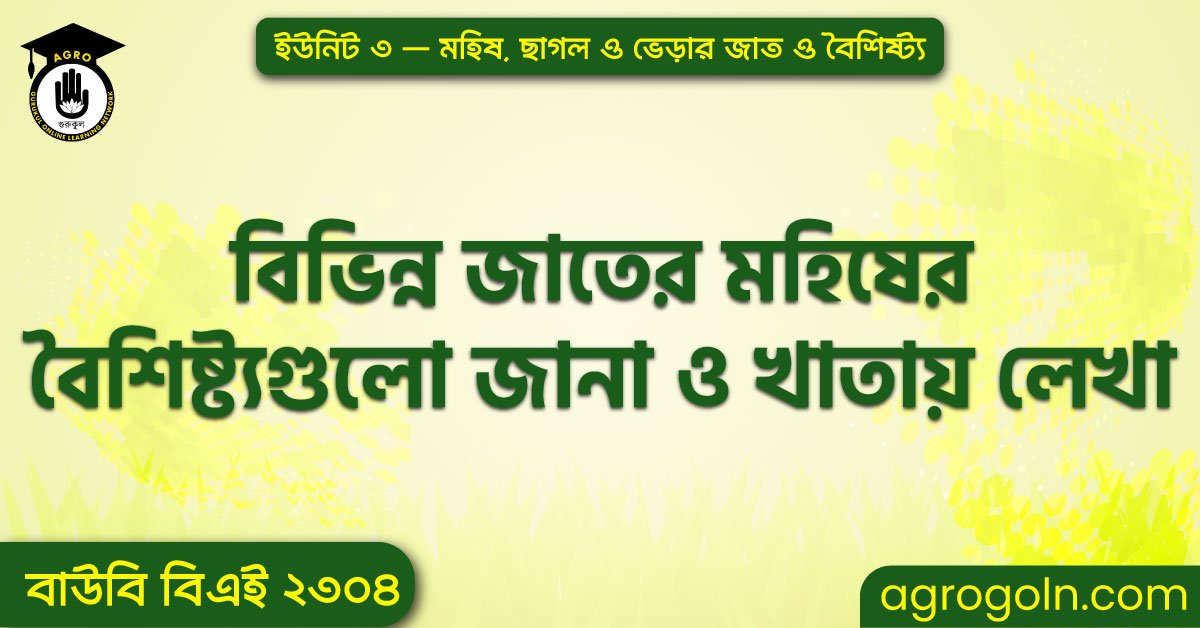মহিষের জাত ও জাতের বৈশিষ্ট্য – কৃষি শিক্ষা ২য় পত্র বিষয়ের এই পাঠটি ১১ নং ইউনিটের ১১.৪ নং পাঠ। এই পাঠে আমরা বিভিন্ন ধরণের মহিষের জাত ও তদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো। মহিষ অন্যতম গৃহপালিত স্তন্যপায়ী। মহিষ মুখ্যত উত্তর গোলার্ধের এক প্রজাতি এবং চেহারায় গরুর সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে। উত্তর আমেরিকার বাইসনকে (bison) অনেক সময় মহিষ বলা হলেও প্রকৃত মহিষের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।
মহিষের জাত ও জাতের বৈশিষ্ট্য
বাংলাদেশের সব এলাকেতেই মহিষ পালন করা হয়ে থাকে। তবে বিশেষ নদীর চর, সমুদ্র উপকূল দ্বীপাঞ্চল এবং হাওর-বাঁওড় এলাকায় মহিষ পালন করা হয় বেশি। এদেশে গৃহপালিত মহিষের সংখ্যা প্রায় ১.৪৭ মিলিয়ন(বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫-২০১৬)। মহিষ প্রধানত হালচাষ ও গ্রামীণ পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। তবে মহিষের দুধ ও মাংস উৎকৃষ্ট খাদ্য। এ ছাড়া মহিষের গোবর জৈব সার ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মহিষের হাড় পন্যসামগ্রী যেমন বোতাম, চিরুনি ইত্যাদি তৈরি এবং গবাদি প্রাণিখাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
মহিষে জাতের শ্রেণীবিভাগ
গৃহপালিত মহিষের জাতগুলোকে আবাসস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি কওে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- জলাভূমি মহিষ বা কাদাপানির মহিষ (Swamp Buffalo) এবং নদী মহিষ বা পরিষ্কার পানির মহিষ (River Buffalo)।
জলাভূমির মহিষ (Swamp Buffalo ):
জলাভূমির মহিষের বুক সাধারণত চওড়া, দেহ মাংসল ও গোলাকৃতির যা দেখতে অনেকটা ব্যারেলের মতো। এদের শিং বেশ চওড়া, লম্বা ও চন্দ্রাকৃতির। ষাঁড় ও গাভীর ওজন সাধারণত যথাক্রমে ৫০০ ও ৪০০ কেজি। ষাঁড় ও গাভীর উচ্চতা
সাধারণত গড়ে ১৩৫ সে.মি, হয়ে থাকে। এদের পা খাটো এবং কপাল ও মুখমন্ডল চ্যাপ্টা। গায়ের রং গাঢ় ধূসর থেকে সাদা হয়। চামড়ার রঙ নীলচে কালো থেকে ধূষর কালো হয়ে থাকে। গলকম্বলের উপরিভাগ থেকে গলার পাদদেশে পর্যন্ত বক্রাকৃতির দাগ থাকে। এরা অত্যন্ত কম দুধ উৎপাদন করে, দৈনিক গড়ে ১ লিটারের মতো যা বাছুরের জন্যই যথেষ্ট নয়। এরা ৩৯৪ দিনে গড়ে মাত্র ৩৩৬ লিটার দুধ দিয়ে থাকে।
শারীরিক বৃদ্ধির হার কম, ফলে বয়: প্রাপ্তি বিলম্বে ঘটে; সাধারণত তিন বছরের পূর্বে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে না। গর্ভকালে ৩২৫—৩৩০ দিন। সাধারণত নিচু কর্দমাক্ত জলাভূমিতে থাকতে পছন্দ করে, কাদায় গড়াগড়ি দেয় এবং জলাভূমি ও আইলের মোটা অঁাশজাতীয় ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এরা প্রধানত শক্তির কাজেই পটু। তাই হাল, মই ও গাড়ি টানার কাজে ব্যবহৃত হয়। দুধ উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম কিন্তু মাংসের জন্য ভালো।
কোয়া কাম ও কোয়াইটুই (Kwua Cum and Kwaitui)
এই দু’জাতের মহিষ থাইল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। কোয়াইটুই মহিষের দেহ দীর্ঘ ও প্রশস্ত। গায়ের রঙ কালো, চামড়া পুরু, মুখমণ্ডল লম্বা। গাভীর গলা সরু। উচ্চতা ও ওজন গড়ে যথাক্রমে ১৪০ সে.মি. ও ৪৫০ কেজির মতো।
কোয়াদুরে মহিষ (Kwa kui)
এরা আকারে তুলনামূলভাবে খাটো। দেহ ও গলা সরু, ঘাড় সরু, মুখমণ্ডল লম্বা। গায়ের রঙ হালকা ধূসর। উচ্চতা ও ওজন গড়ে যথাক্রমে ১৩০ সে.মি ও ৩৫০ কেজির মতো। এরা হাল-চাষ ও ভারবাহী জন্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
কোয়াইয়া (Quipra)
এই উপজাতের মহিষ ধাইল্যান্ডের মি সড টক (Mae Sod Tak) অঞ্চলে দেখা যায়। এরা আকারে ছোট। ওজন ৩০০-৩৫০ কেজির মতো। বন্য স্বভাবের কারণে এদের কদর তুলনামূলকভাবে কম।
ম্যারিড (Marid)
এই উপজাতের মহিষ মায়ানমারে দেখা যায়। মায়ানমারের সমতলভূমির মহিষ থেকে এরা আকারে ছোট। দেহের কালো লোমগুলো দীর্ঘ, সরু ও খাড়া। ধড় ও গাভীর ওজন গড়ে যথাক্রমে ৩০০ ও ৩২৫ কেজির মতো।
লাল মহিষ (Red Buffalo )
এই উপজাতের মহিষ থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে দেখা যায়। এদের দেহ ঘন ও লম্বা লাল রঙের লোমে আবৃত থাকে। তাই এদের নাম লাল মহিষ। এদের দৈহিক ওজন গড়ে সাধারণত ৩৫০ কেজি হয়ে থাকে। তবে, গায়ের রঙ, দেহের গঠন ও ব্যবহারর দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলাভূমির মহিষের সঙ্গে ভারতের আসামের পশ্চিমাঞ্চলের মহিষের পার্থক্য দেখা যায়।
এদের গায়ের রঙ কালো। শিং অনেকটা কাস্ত্রের মতো থাকা। এরা প্রধানত দুধ উৎপাদনকারী জাত। বিজ্ঞানী মিলেণর ১৯৩৯ সালে এদেরকে নদীর মহিষ হিসেবে নামকরণ করেন। এদের উৎপত্তি ভারত ও পাকিস্তানে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চালেও এদের দেখতে পাওয়া যায়।
মনিপুরি মহিষ
উৎপত্তি ও প্রাপ্তিস্থান
আসামের অন্তর্গত মনিপুর এদের আদি বাসস্থান। আসামের প্রায় সর্বত্র এবং বাংলাদেশের সিলেটে দেখতে পাওয়া যায়।
জাত বৈশিষ্ট্য:
এদের গায়ের রঙ ধূসর। এরা সুঠাম দেহের অধিকারী। মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট। শিং বড় এবং ভেতরের দিকে বাঁকানো। এরা সব রকমের খাদ্যে অভ্যস্থ। এদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। ধাড় ও গাভীর ওজন যথাক্রমে প্রায় ৫০০ ও ৬০০ কেজি।
নদীর মহিষ:
নদীর মহিষের বুক প্রশস্ত, দেহ সাধারণত মাংসল ও অপেক্ষাকৃত কম গোলাকৃতির। শিংয়ের আকার ও আকৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে। ভারত এবং পাকিস্তানে নদীর মহিষের অনেকগুলো জাত দেখা যায়। মহিষ ষাড় ও গাভীর ওজন যথাক্রমে ৩০০-৭০০ ও ২৫০-৬৫০ কেজি হয়।
সাধারণত মহিষ ষাঁড় ও গাভীর উচ্চতা যথাক্রমে ১২০-১৫০ ও ১১৫-১৩৫ সে.মি. হয়। নদীর মহিষের দেহ তুলনামূলকভাবে লম্বা, বুকের বেড় কম, পা খাটো, মাথা ভারি, কপাল প্রশস্ত ও মুখাকৃতি লম্বা। নদীর মহিষের শিংয়ের আকার জলাভূমির মহিষের মতো নয় এবং শিংয়ের অবস্থান ঠিক কপালের একই জায়গায় নয়। এই মহিষের শিং দু’প্রকার। যথা- গোলাকৃতি ও সোজা। এরা সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র স্থানে বাস করতে পছন্দ করে এবং পানির মধ্যে দেহ ডুবিয়ে রাখে। বিভিন্ন জাতের নদীর মহিষের মধ্যে মুররা, নীলি, রাভি, সুরাটি, মেশানা, জাফরাবাদি ইত্যাদি প্রধান। এখানে নদীর মহিষের কয়েকটি জাতের উৎপত্তি, প্রাপ্তিস্থান ও বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।
উন্নত জাতের মহিষের মধ্যে মুররা, নিলি রাভি, মনিপুরী, জাফরাবাদী, নাগপুরী, কুন্ডি, সুরাটি, টোডো, মন্ডা, সম্বলপুরী, টরাই, মেহসানা উল্লেখযোগ্য। মুররা, নিলি রাভি জাতের মহিষ সরকারী খামারে ( মহিষ প্রজনন খামার, বাগেরহাট) পালন করা হয়।
নীলি মহিষ :
এ জাতের মহিষের সাথে মুররা মহিষের বেশ মিল আছে। এদের অনেক বৈশিষ্ট্য প্রায় এক রকম। বিজ্ঞানীদের মতে মুররা জাত থেকেই এদের উদ্ভব হয়েছে। তবে আকার, মুখাকৃতি ও কপালের মধ্যে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। পাকিস্তানের মন্টগোমারি জেলার শতদ্রু নদীর উভয় পাশে এদের আদি বাসস্থান। ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে নীলি জাতের মহিষ পাওয়া যায়। শতদ্রু নদীর নীল পানির বর্ণনায় এদের নামকরণ নীলি রাখা হয়েছে।
জাত বৈশিষ্ট্য:
এদের গায়ের ও পশমের রং কালো। কিন্তু ১০—১৫% বাদামি রঙেরও দেখা যায়। দেহাকৃতি মাঝারি ধরনের। কপাল, মুখ, থুতনি, পা এবং লেজের অগ্রভাগে সাদা চিহ্ন দেখা যায়। অনেকটা লম্বাকৃতির মাথার উপরিভাগ স্ফীত এবং দুচোখের মধ্যবর্তী স্থান একটু চাপা। ওলান এবং সিনায় মাঝে মাঝে পিঙ্গল চিহৃ দেখা যায়। শিং ছোট ও শক্তভাবে প্যাঁচানো ঘাড় লম্বা, চিকন ও মসৃণ। ওলান উন্নত লেজ লম্বা। ষাঁড় ও গাভী মহিষের গড় উচ্চতা যথাক্রমে ১৩৭ ও ১২৭ সে.মি. এবং দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৫৭ ও ১৪৭ সে.মি.।
উৎপত্তি ও প্রাপ্তিস্থান
পাকিস্তানের মন্টগোমারি জেলার শতদ্রু নদীর উভয় পার্শ্বে এদের আদি বাসভূমি। ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে নীলি জাতের মহিষ পাওয়া যায়৷ শতদ্রু নদীর নীল পানির বর্ণনায় এদের নামকরণ নীলি রাখা হয়েছে।
রাভি মহিষ :
এ জাতের মহিষ দুধের জন্য প্রসিদ্ধ। পাক—ভারতের অন্তর্গত রাভি নদীর উভয় পাশে^র্ এদের আদি বাসভূমি। এজন্য এদের নাম রাভি রাখা হয়েছে। পাকিস্তানের লায়ালপুর জেলা, ওকারা, মন্টগোমারি, ভারতের গুজরাট ও চিনাব নদীর উপতাকায় এবং ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এদের পাওয়া যায়।
জাত বৈশিষ্ট্য:
রাভি মহিষ বৃহদাকৃতির দেহের অধিকারী। গাভীর মাথা মোটা ও ভারি। মাথার মধ্যভাগ উত্তল, শিং প্রশস্ত, মোটা ও কোকড়ানো। থুতনি স্পষ্ট, ওলান সুগঠিত। লেজ বেশ লম্বা এবং প্রান্তদেশে সাদা লোম আছে। গায়ের রং কালো, তবে কোনো সময় বাদামি রঙেরও হয়। ষাঁড় ও গাভী মহিষের উচ্চতা যথাক্রমে ১৩২ ও ১২৭ সেমি এবং দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৫৪ ও ১৪৯ সেমি এবং ওজন যথাক্রমে ৬০০ ও ৬৪৫ কেজি।
মুররা মহিষ :
এ জাতের মহিষের উৎপত্তিস্থল ভারতের উত্তর—পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে, দিল্লির আশপাশ এলাকা। বর্তমানে পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে এ জাতের মহিষ বেশি পাওয়া যায়। এটি দুগ্ধপ্রদানকারী বিশেষ জাত।
বৈশিষ্ট্য:
১. এদের দেহ আকারে বেশ বড় হয়।
২. শিং ছোট এবং বাঁকানো হয়।
৩. গায়ের রং সাধারণত কালো হয়।
৪. স্ত্রী মহিষের পিছনের তুলনায় সম্মুখ ভাগ হালকা হয়।
৫. এরা দুধের জন্য প্রসিদ্ধ।
৬. একটি গাভী মহিষ দিনে প্রায় ২২—২৭ লিটার দুধ দিয়ে থাকে।
৭. কপাল বড়, চওড়া ও উন্নত।
৮. পা খাটো, মোটা এবং ওলানগ্রন্থি খুব বড়।
৯. দেহের পশ্চাৎ ভাগ অপেক্ষাকৃত চওড়া ও ভারী।
১০. গাভী ও ষাঁড়ের ওজন কম বেশি ৫৬৭ ও ৫৩০ কেজি।
১১. বলদ মহিষ হালচাষ ও গাড়ি টানার কাজে ব্যবহৃত হয়।
১২. বাঁট লম্বা, সামনের বাঁটের চেয়ে পিছনের বাঁট লম্বা। চিত্র ১১.৪.২ : মুররা
১৩. বাৎসরিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০—৩০০০ লিটার।
জাফরাবাদি মহিষ
জাফরাবাদি গাভী দুধ উৎপাদনকারী এবং ষাঁড় চাষাবাদ ও গাড়ি টানার জন্য বিখ্যাত।
উৎপত্তি ও প্রাপ্তিস্থান
ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের গুজরাট, গির অরন্য ও জাফরাবাদ শহরের আশেপাশে এই জাতের মহিষ দেখা যায়। জাফরাবাদের নামানুসারে এদেরকে জাফরাবাদি বলা হয়।
জাত বৈশিষ্ট্য
এরা আকারে বড়, দেহ গভীর ও সুগঠিত। কপাল স্ফীত, শিং ভারি এবং চ্যাপ্টা। গায়ের রঙ কালো তবে মুখ, পা এবং লেজে সাদা দাগ দেখা যায়। ঘাড় মাংসল, গলকম্বল ও ওলান সুগঠিত। এদের দেহ লম্বাটে, পা লম্বা ও সরু, লেজ খাটো। ষাঁড় ও গাভী মহিষের ওজন যথাক্রমে ৫৯০ ও ৪৫০ কেজি। গাভী দিনে গড়ে ১৫-২০ লিটার দুধ দেয়। দুধে চর্বির পরিমাণ খুব বেশি। ষাড় চাষাবাদ ও গাড়ি টানার কাজে ব্যবহৃত হয়।
মেশানা মহিষ
উৎপত্তি ও প্রাপ্তিস্থান
গুজরাট প্রদেশের বারোদা অঞ্চল ও মেশানা জেলা এদের আদি বাসস্থান। মুররা এবং সুরাটি মহিষের সংকরায়নের মাধ্যমে মেনশানা জাতের উৎপত্তি ।
জাত বৈশিষ্ট্য
এরা মুররা এবং সুরাটি মহিষের মধ্যবর্তী, দেহে দু’জাতেরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। গায়ের রঙ কালো, বাদামি বা ধূসর। মুখমন্ডল, পা এবং লেজের অগ্রভাগে সাদা দাগ আছে। দেহ লম্বা এবং সুগঠিত। কপাল প্রশস্ত্র, মাঝের অংশ কিছুটা নিচু, শিং কোকড়ানো এবং দেখতে কাস্ত্রের মতো কান মাঝারি এবং অগ্রভাগ চোখা।
ঘাড় মাংসল, সুগঠিত, গলকম্বল নেই। বুক প্রশস্ত, কাঁধ চওড়া এবং দেহের সাথে সুবিনাস্ত্র, পা মাঝারি আকারের। ওলান সুগঠিত ও উন্নত। ষাঁড় ও গাভীর ওজন যথাক্রমে ৪৫০ ও ৬৫০ কেজি। এই জাতের মহিষ ভারতের গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে দুধ ও ঘি সরবরাহের জন্য সুপরিচিত। দুধ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। এরা নিয়মিত বাচ্চা প্রদানের জন্যও বিখ্যাত।
বাংলাদেশের মহিষ:
বর্তমানে বাংলাদেশে মহিষের সংখ্যা প্রায় ৬,২১,৪৭। এর মধ্যে প্রায় ৫৪,০০০ মহিষ শক্তির কাছে নিয়োজিত থাকে। তবে এদেশে মহিষের কোনো উল্লেখযোগ্য জাত নেই । উপকূলীয়, হাওর এবং আখ উৎপাদনকারী এলাকাসমূহে মহিষের বিস্তৃতি তুলনামূলক ভাবে বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশের মহিষকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— নদী, জলাভূমি এবং নদী ও জলাভূমির মহিষের সংকর। দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যে সমতলভূমিতে নদীর মহিষ দেখা যায়। এরা প্রধানত ভারতের দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের মহিষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দেশের পূর্বাঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকায় জলাভূমির মহিষ ও সংকর মহিষের অবস্থান।
দূরপ্রাচ্যের জলাভূমির মহিষ ও আদি মহিদের সাথে এদের বেশ মিল রয়েছে। বাংলাদেশের জলাভূমির মহিষ মূলত শক্তির কাজে ব্যবহৃত হয়। এদের দুধ উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম। দক্ষিণাঞ্চলে ছোট ছোট কৃষক পরিবারে ১-৪টি পর্যন্ত মহিষ দেখতে পাওয়া যায়। গাভী দিনে ১-৩ লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। দুধ প্রধানত মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গরুর দুধের চেয়ে মহিষের দুধ বাজারে কম দামে বিক্রি হয়।
দুধে স্নেহের ভাগ বেশি। গবাদিপশুর মাংসের মধ্যে মহিষের মাংস বাজারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গাড়ি টানা, ঘানি টানা, হালচাষ, সেচকার্য, ধান মাড়াই প্রভৃতি শক্তির কাছে এরা ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের মহিষ প্রধানত দেশী মহিষ হিসেবেই পরিচিত। দেহের আকার, পাড়েন এবং রঙের দিক থেকে এদের মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শিংয়ের আকার এবং পড়নও ভিন্নতর। প্রাণিজ আমিষজাতীয় খাদ্যের চাহিদা, পশুশক্তির ঘাটতি প্রভৃতি মেটানোর জন্য উন্নত প্রজনন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এদেশের মহিষের উন্নতি অত্যাবশ্যক।
অনুশিলন:
আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-বিভিন্ন জাতের মহিষের বৈশিষ্ট্যগুলো জানা ও খাতায় লেখা।
এই পাঠ শেষে আপনি-
- দেশী মহিষের আকার, আকৃতি বলতে পারবেন।
- দেশী মহিষের সাথে উন্নত জাতের মহিষের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- গরু ও মহিষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
প্রাসঙ্গিক তথ্য
বাংলাদেশের সিলেট জেলায় মনিপুরি মহিষ দেখা যায়। এরা প্রধানত মাংস উৎপাদন, হালচাষ বা পরিবহণের জন্য উপযোগী। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো কোনো অঞ্চলে মুররা জাতের কিছু মহিষ দেখা যায়। মুররা ও মনিপুরি জাতের মধ্যে দৈহিক এবং উৎপাদনগত পার্থক্য নিরূপন করা যায়।
মহিষ ও গরুর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়। মহিষের গলকম্বল নেই, দেহে লোম খুব কম, জলাভূমির মহিষের শিং বড় ও অনেকটা কাস্ত্রের ন্যায়। তাছাড়া আকারে মহিষ সাধারণত গরু থেকে বড় হয়ে থাকে। এছাড়া বাকি সবগুলো বৈশিষ্ট্য মহিষের ক্ষেত্রে গরুর মতোই।
প্রয়োজনীয় উপকরণ
একটি মহিষ ষাড় বা গাভী, কলম, পেন্সিল, রাবার, ব্যবহারিক খাতা ইত্যাদি।
কাজের ধাপ
- প্রথমে একটি মহিষ দেখে তার অঙ্গপ্রতঙ্গের নাম জানুন ও খাতায় আঁকুন ।
- যেসব কৃষকের বাড়িতে মহিষ আছে তাদের বাড়ি যান এবং প্রত্যক্ষভাবে মহিষের আকার,
- আকৃতি ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করুন। মহিষের জাতসমূহের বৈশিষ্ট্যের সাথে আপনার দেখা মহিষের
- বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখুন এবং ব্যাবহারিক খাতায় লিখুন।
- মহিষ দেখার পর তার জাত বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।
সতর্কতা
প্রত্যক্ষভাবে মহিষ দেখার সময় সতর্কতার সাথে অগ্রসর হোন।
সারমর্ম :
বাংলাদেশের সিলেট জেলায় মনিপুরি মহিষ আছে যা প্রধানত মাংস উৎপাদন, হালচাষ বা পরিবহণের জন্য উপযোগী। এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে মুররা জাতের মহিষও দেখা যায়। মহিষ ও গরুর মধ্যে পার্থক্য অল্প। মহিষের গলকম্বল নেই, দেহে লোম কম, জলাভূমির মহিষের শিং বড় ও কাস্তের ন্যায়। সাধারণত আকারেও এরা বড় হয়ে থাকে। এছাড়া বাকি বৈশিষ্ট্যগুলো গরুর মতোই।