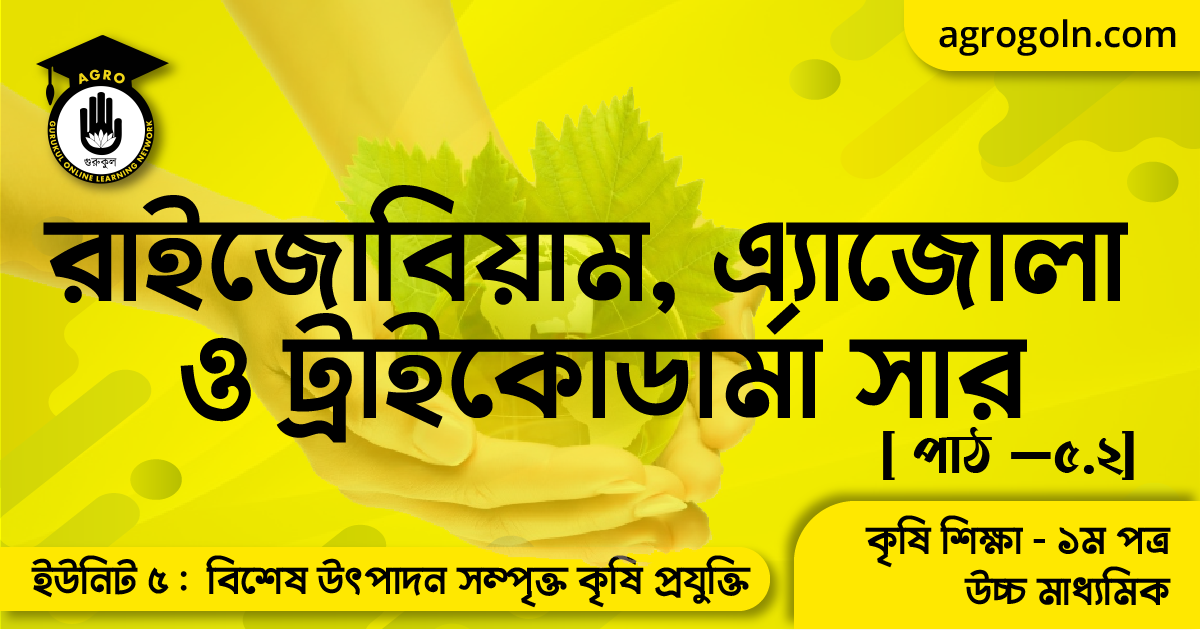রাইজোবিয়াম, এ্যাজোলা ও ট্রাইকোডার্মা সার – আজকের আলোচনার বিষয়। এই পাঠটি “বিশেষ উৎপাদন সম্পৃক্ত কৃষি প্রযুক্তি” বিষয়ের ৮ নং ইউনিটের ৮.১ নং পাঠ।
রাইজোবিয়াম, এ্যাজোলা ও ট্রাইকোডার্মা সার
রাইজোবিয়াম:
১. রাইজোবিয়াম কি ?
রাইজোবিয়াম এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া শিম ও ডাল জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের কাছে অবস্থান নিয়ে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্রহন করে শিকড়ে গুটি তৈরি করে। এ ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংযোজন করে নিজের প্রয়োজন মিটায় এবং উদ্ভিদে সরবরাহ করে।
শিম জাতীয় উদ্ভিদ যেমন— মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, সয়াবিন, চিনাবাদাম, ধইঞ্চা ইত্যাদি ফসলে ব্যাকটেরিয়া সার ব্যবহার করে উত্তম ফসল পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী রাইজেবিয়াম অণুজীব সার ইউরিয়া সারের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়।
২. রাইজোবিয়াম অণুজীব সার তৈরীর পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো:
১। রাইজোবিয়াম প্রজাতি নিবার্চন:
রাইজোরিয়াম প্রজাতি শিম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে নডিউল থেকে সরাসরি আলাদা করে গবেষণাগারে সংরক্ষণ করা হয়। সংগৃহীত রাইজোবিয়াম প্রজাতি কতোগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ করা হয়। এ কাজের জন্য প্রথমে বিভিন্ন মৃত্তিকায় সুপারিশকৃত উদ্ভিদকে কার্যকরী নডিউল তৈরী করতে সক্ষম হতে হবে। এছাড়া উক্ত উদ্ভিদটির অনুপস্থিতিতে প্রজাতির মাটিতে টিকে থেকে বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
২। আবাদ মাধ্যম:
রাইজোবিয়ামের বংশবৃদ্ধির জন্য সাধারণত দুই ধরনের আবাদ মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। কঠিন মাধ্যম ও তরল মাধ্যম।
কঠিন মাধ্যম :
কঠিন আবাদ মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে— পিটমাটি, কাঠের গুড়া ও ছাই। জীবাণু যাতে জীবাণুসারে দীর্ঘদিন টিকে থাকে, কার্যকর থাকে এবং ব্যবহারের সুবিধা বিবেচনায় আবাদ মাধ্যমের যাথেষ্ট পানি ধারণক্ষমতা ও প্রচুর কার্বন থাকতে হবে।
তরল মাধ্যম :
প্রথমে তরল আবাদ মাধ্যম প্রস্তুত করতে হবে। প্রয়োগোপযোগী অণুজীবের চাষ করতে হবে। এরপর তরল মাধ্যমটি ১৫ পাউন্ড চাপে (১২১ সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) ৩০ মিনিট ধরে নিবীর্জ করা হয় এবং ঠান্ডা করে তরল মাধ্যমে নিবার্চিত অনুজীব (রাইজোবিয়াম) জন্মানো হয়।
তরল কালচারকে ২৮ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে অনবরত কিছুক্ষণ ঝাঁকুনি দিলে ভিতরের তরল মাধ্যমে অক্সিজেন প্রবেশ করে প্রচুর অণুজীব উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। অত:পর এ অণুজীব তরল অব¯ায় বাহ’ কের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়। যথেষ্ট সংখ্যক অণুজীব (১০৬ ১০৯/মিলিলিটার) জন্মানোর পর পরিমাণমত তরল কালচার নিবীর্জ করা পিট মাটির সাথে মেশানো হয়।
৩। পীট মাটি তৈরী :
পিট মাটি সংগ্রহের পর রোদে শুকানো হয়। কোন আবর্জনা বা পাথর থাকলে তা ভালভা ব পরিস্কার করে প্রথমে হাতুড়ি দিয়ে ও পরে মেশিনের সাহায্যে গুড়া করা হয়। রাইজোবিয়াম জন্মানোর জন্য ৭৫ মাইক্রোমিটার বিশিষ্ট চালুনি দিয়ে পিটের গুঁড়া চালা হয় এবং এতে শতকরা ২—৩ ভাগ ক্যালশিয়াম কার্বনেট মেশাতে হয় যাতে অম্লমান ৬.৫—৭.৩ হয়।
পলিথিনের ব্যাগে ভরে (সাধারণত ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম) তা অটোক্লেভে দিয়ে নির্দিষ্ট সময় ও তাপে নিবীর্জ করা হয়। এরপর গামা রেডিয়েশন দিয়ে পিট মাটি জীবাণুমুক্ত করা হয়। এভাবে তৈরি পিট মাটির প্যাকেটে পরিমাণ মতো তরল মাধ্যমে জন্মানো অণুজীব সতর্কতার সাথে সিরিঞ্জের সাহায্যে প্রবেশ করানো হয় যাতে নতুনভাবে অনাকাক্সিক্ষত অণুজীব ব্যাগে ঢুকতে না পারে। তরল অণুজীব কালচার ও পিট মাটি ভালভাবে মিশিয়ে কয়েকদিন রাখা হয় যা পরবতীর্তে বীজের সাথে মিশিয়ে ব্যবহারের জন্য বাজারজাত করা হয়।
অণুজীব সার জমিতে ব্যবহার পদ্ধতি :
নিচে অণুজীব সারের প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :
১। অণুজীব সার বীজের সাথে মেশানোর সময় আঠালো বস্তু হিসাবে চিটাগুড়, ভাতের ঠান্ডা মাড় অথবা পানি ব্যবহার করতে হয়, তবে পানি ব্যবহার না করাই ভালো।
২। ব্যবহৃত বীজে যদি কোনরূপ কীটনাশক ব্যাবহার করা হয়ে থাকে তবে সেই বীজ পানিতে ভালভাবে ধুয়ে অণুজীব সার মেশাতে হবে।
৩। উত্তম ও সুস্থ সবল বীজ পরিমাণমতো একটি পলিথিন ব্যাগ বা পাত্রে নিয়ে তাতে চিটাগুড় বা ভাতের মাড় মিশিয়ে এমনভাবে নাড়তে হবে যাতে প্রতিটি বীজের গায়ে প্রলেপ পড়ে।
৪। এ প্রলেপযুক্ত বীজের সাথে অণুজীব সার এমনভাবে মেশাতে হবে যাতে প্রতিটি বীজে কালো বর্ণের প্রলেপ পড়ে।
৫। অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ সকাল ৯ টার মধ্যে বা বিকাল ৪ টার পর বপন করে যত দ্রুত সম্ভব মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
৬। কোন নির্দিষ্ট ফসলের বীজ আধা ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে সেই পানি ফেলে দিতে হবে। অত:পর রাইজোবিয়াম অণুজীব ঐ বীজের উপর ঢেলে দিয়ে তা ভালোভাবে ছিটিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
৭। বীজের গায়ে যাতে সূর্যের আলো না লাগে সেদিকে খেয়াল করতে হবে। সূর্যের আলো লাগলে অণুজীব মারা যাবে
এবং অণুজীব সার প্রয়োগ ব্যর্থ হবে।
এ্যাজোলা:
এ্যাজোলা হচ্ছে ভাসমান জলজ পানা। যা পুকুর, ডোবা, নালা, ধানের জমিতে ভাসমান অবস্থায় থাকে। এ্যাজোলার দৈহিক ওজন প্রতি ৫ দিনে দ্বিগুন হতে পারে। এ্যাজেলা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০০—৫০০ কেজি নাইট্রোজেন যোগ করা যেতে পারে। বোরো ধানের জমিতে অতি সহজ ও সফলভাবে এ্যাজোলা চাষ করা যায়। এ্যাজোলা মাটির উর্বরতা ও গুনাগুনের উন্নয়ন ঘটায়।
এ্যাজোলা ব্যবহার করলে সালফার ও জিংকের ঘাটতিও দূর হয়। এ্যাজোলার পাতার গহ্বরে অ্যানাবিনা এ্যাজোলি নামক নীলাভ সবুজ শেওলার একটি প্রজাতি মিথোজীবীরূপে বাস করে যা বায়ুমন্ডল থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন সংযোজন করে এ্যাজোলার পাতার গহ্বরে জমা করে। এ এ্যাজোলা মাটিতে চাষ দিয়ে মেশালে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ হয়।
চাষ পদ্ধতি :
অতি ঠাণ্ডা কিংবা অতি গরম আবহাওয়ায় অ্যজোলা জন্মাতে পারে না। বাংলাদেশে বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এর চাষ করার উপযুক্ত সময়। যে জমিতে ধান চাষ করা হবে এমন জমি এ্যাজোলা চাষের জন্য নির্বাচন করা প্রয়োজন। অ্যাজোলার চাষ পদ্ধতি নিম্নরূপ—
১। প্রথমে ৫ বা ৬ সেন্টিমিটার পানি দাঁড়ানো একখন্ড জমি নির্বাচন করে ভালভাবে চাষ বা মই দিয়ে সমান ৮টি প্লটে ভাগ করে নিতে হয়।
২। উক্ত জমির দুইকোণার দুইটি প্লটে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ৫০০—৮০০ গ্রাম হিসেবে তাজা এ্যাজোলা ছেড়ে দিতে হয়।
৩। অ্যাজোলা ছাড়ার আগে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ২.০ গ্রাম কার্বোফোরান—৫ জি প্রয়োগ করতে হয়।
৪। এ্যাজোলা ছাড়ার পর জমির পানি পরিষ্কার হলে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ০.৮—১.৬ গ্রাম টিএসপি সার পানিতে গুলে এ্যাজোলার উপর সরাসরি প্রয়োগ করতে হয়।
৫। এ্যাজোলা যথেষ্ট ঘন হলে পাশের প্লটে এ্যাজোলা ছেড়ে অনুমোদিত পরিমাণ ও পদ্ধতিতে কার্বোফোরান ও টিএসপি প্রয়োগ করতে হয়।
৬। এভাবে এক মাসের মধ্যে সমস্ত জমিটি এ্যাজোলায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়।
উপকারিতা :
এ্যাজোলা ব্যবহারের উপকারিতাসমূহ নিম্নরূপ। যথা—
১। এ্যাজোলা সার মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে নাইট্রোজেন যোগ করে। বিশেষ করে ধান ক্ষেতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন সঞ্চয়ন করে।
২। এ্যাজোলা ধানের সাথে একত্রেই জন্মানো যায়; কিন্তু তা ধানের বৃদ্ধিতে কোন ব্যাঘাত ঘটায় না।
৩। এ্যাজোলা অধিক পানিতে জন্মাতে পারে।
৪। এ্যাজোলা আগাছা দমন করে।
৫। উঁচু জমির ফসলে এ্যাজোলা কম্পোষ্টের উপাদান যোগান দেয়। যে সব ফসল জলবদ্ধ অবস্থায় জন্মাতে পারে না। সে সব জমিতে এ্যাজোলা কম্পোষ্ট হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
৬। প্লাবিত এলাকায়, যেখানে সবুজ সার শস্য জন্মানো যায় না, সেখানে এ্যাজোলা জন্মানো যায়।
৭। এ্যাজোলা মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
৮। এ্যাজোলা ব্যবহার করলে প্রতি হেক্টর জমিতে ৩০—৪০ কেজি নাইট্রোজেন কম লাগে।
৯। এ্যাজোলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
এ্যাজোলা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা :
এ্যাজোলা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নরূপ—
১। জমিতে অবশ্যই পানি আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে হবে।
২। উচ্চ তাপমাত্রায় এ্যাজোলার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৩। এ্যাজোলাতে কীট—পতঙ্গের আক্রমণ অধিক।
৪। বছরের সব মৌসুমে এ্যাজোলা জন্মানো খুব কঠিন।
৫। শামুক এ্যাজোলা খেয়ে ফেলতে পারে।
৬। ফসফরাস প্রয়োগ ব্যতীত এ্যাজোলা উৎপাদন কঠিন।
৭। কম্পোষ্ট সার হিসাবে এ্যাজোলাকে কোন ক্ষেতে প্রয়োগ করতে গেলে পরিবহন করা ঝামেলাপূর্ণ হয়।
ট্রাইকোডার্মা :
ট্রাইকোডার্মা এক প্রকার ছত্রাক। এ ছত্রাক বিভিন্ন ময়লা আবর্জনার সাথে ব্যবহার করে যে সার তৈরি করা হয় তাকে ট্রাইকোডার্মা অণুজীব সার বলে। ২৫—৩০ সে তাপমাত্রায় এ ছত্রাক বংশবিস্তার করতে পারে। পচনশীল দ্রব্য বিয়োজনের মাধ্যমে এর জীবন চক্র সম্পন্ন হয়। ট্রাইকো কম্পোষ্ট তৈরিতে ট্রাইকোর্ডামা ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠে।
এই ছত্রাকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এটি অন্যান্য অণুজীবের বা ছত্রাকের চেয়ে কঠিন বস্তু যেমন কাঠের গুড়া গাছের শক্ত অংশ বিয়োজন করতে পারদর্শী। মাটিতে এর কোন নেতিবাচক প্রভাব নেই। তাই এটি পরিবেশ বান্ধব। এ ছত্রাক গাছে রোগ সৃষ্টিকারী অনেক রোগজীবাণু খেয়ে ফেলে এবং গাছের সুরক্ষা দেয়। এজন্য একে ডক্টরস্ ফাংগাস বলা হয়।
ট্রাইকোর্ডামা সার তৈরীর পদ্ধতি :
১। প্রথমে মাটিতে ১ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১ মিটার প্রস্থ করে কয়েকটি গর্ত তৈরী করতে হবে গর্তের গভীরতা হবে ১ হাত বা ০.৫ মিটার।
২। অত:পর বাড়ির ময়লা আবর্জনা, পৌরসভার বর্জ্য ইত্যাদি হতে অপচনশীল দ্রব্য। যেমন— পলিথিন, ইট, পাথর ও লোহার টুকরা ইত্যাদি আলাদা করতে হবে।
৩। বৃষ্টির পানি রোধে গর্তের চারধারে আইল দিতে হয়। রোদের তীব্রতা ও ঝড়বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে গ র্তর উপর ঢাকনা দিতে হয়। আবর্জনা গর্তে ফেলার আগে একটু গোবর মেশালে ভাল হয়। শুকনো হলে সামান্য পানি ছিটাতে হয়।
৪। অত:পর প্রতিটি গর্তের জন্য ১৫০ মি.লি. ট্রাইকো সাসপেনশন তৈরি করতে হবে। গর্তে বর্জ্য তিন ধাপে ঢালতে হবে এবং প্রতিটি ধাপে/স্তরেই ট্রাইকোডার্মা সাসপেনশন স্প্রে করতে হবে।
৫। গর্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেলে সমস্ত গর্তের বর্জ্য ভালভাবে মেশাতে হবে।
৬। বৃষ্টি বা প্রচণ্ড রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
৭। সমভাবে পচনের জন্য ৭ দিন অন্তর অন্তর আবর্জনা উল্টে—পাল্টে দিতে হবে।
৮। ৫—৬ সপ্তাহ পর আবর্জনা চা পাতার মত ঝরঝরে ও গন্ধহীন হয়ে ব্যবহার উপযোগী হয়।